
VOICE OF BENGAL
বাংলার পাতা
আমি বাংলায় কথা বলি, বাংলায় গান গাই।বাংলায় লিখি, বাংলায় পড়ি। নাম আমার সুভাষ চ্যাটার্জি। নিবাস সল্টলেক, কোলকাতা।যাঁরা বাংলা ভালবাসেন, সাহিত্য সৃষ্টি করেন–পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, তাঁদের সকলের জন্যই এই পাতাকে উৎসর্গ করলাম। আসুন, বিনামূল্যে সারা পৃথিবীর সমস্ত বাংলাভাষী মানুষের কাছে আপনার সাহিত্যকীর্তি পৌঁছাতে হাত মেলান।

বাংলার পাতা~~কয়েকটি কথা
সকল বাংলাপ্রেমী মানুষের মিলনমেলা
২০২২ এর সেপ্টেম্বরে আমাদের যাত্রা হলো শুরু। বন্ধুবান্ধব, পরিচিত সকলকে নিয়ে হাত ধরে এগোতে চাই। বাংলা ছড়া, কবিতা, গল্প–এ সব নিয়েই চলবে আমাদের আসর। শুধু অনুরোধ, শালীনতা বজায় রেখে লিখুন এবং ব্যক্তিগত আক্রমন নয়। আসুন, লিখুন, পড়ুন, ভাবের বিনিময় করুন। banglarpataxyz@gmail.com এ ইমেল করে নাম, ঠিকানা সহ মৌলিক রচনা পাঠান।
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা , বাংলা মাতৃদুগ্ধ বাংলা আমার মায়ের কোল - উষ্ণ,কোমল, স্নিগ্ধ
Contact Us


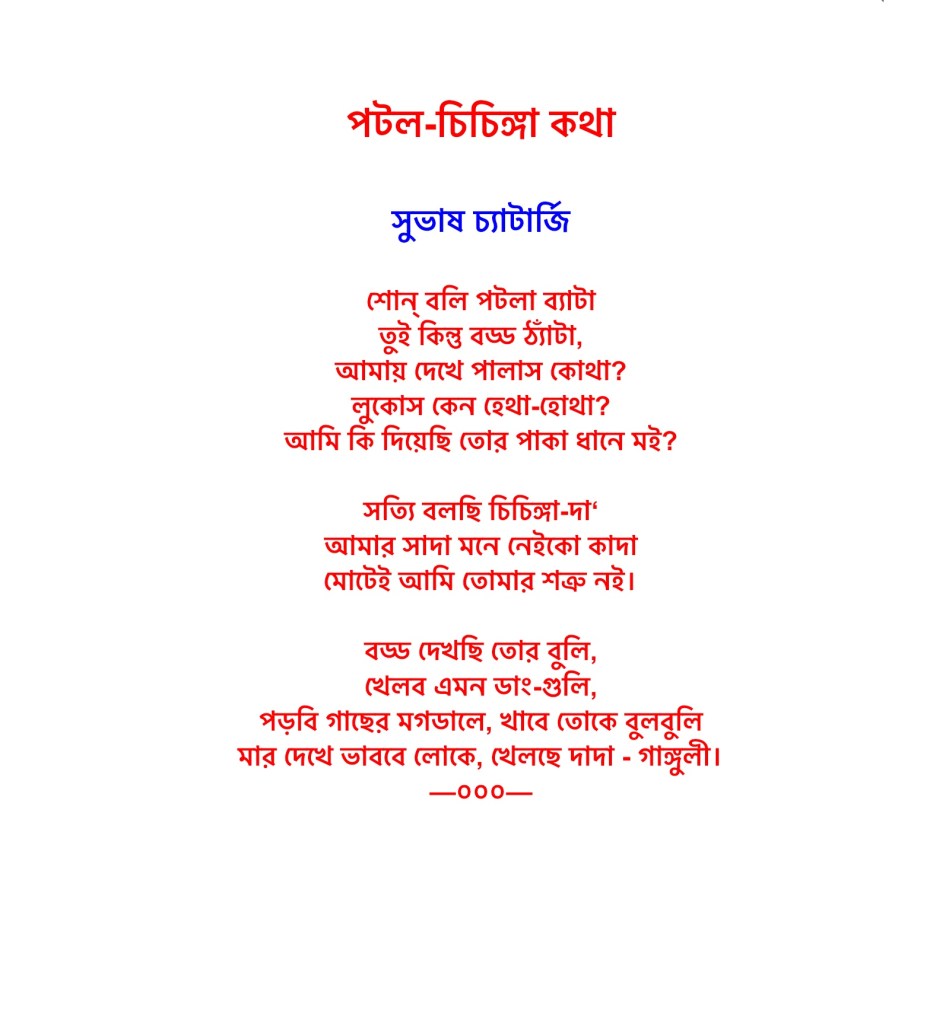

P6
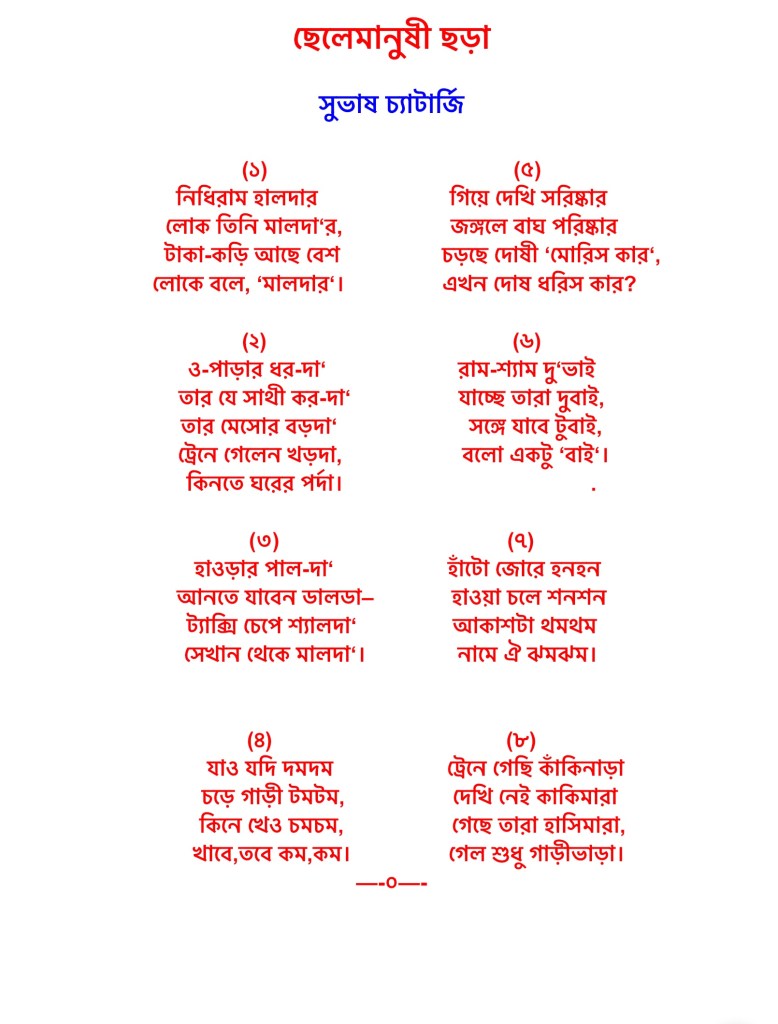
P7
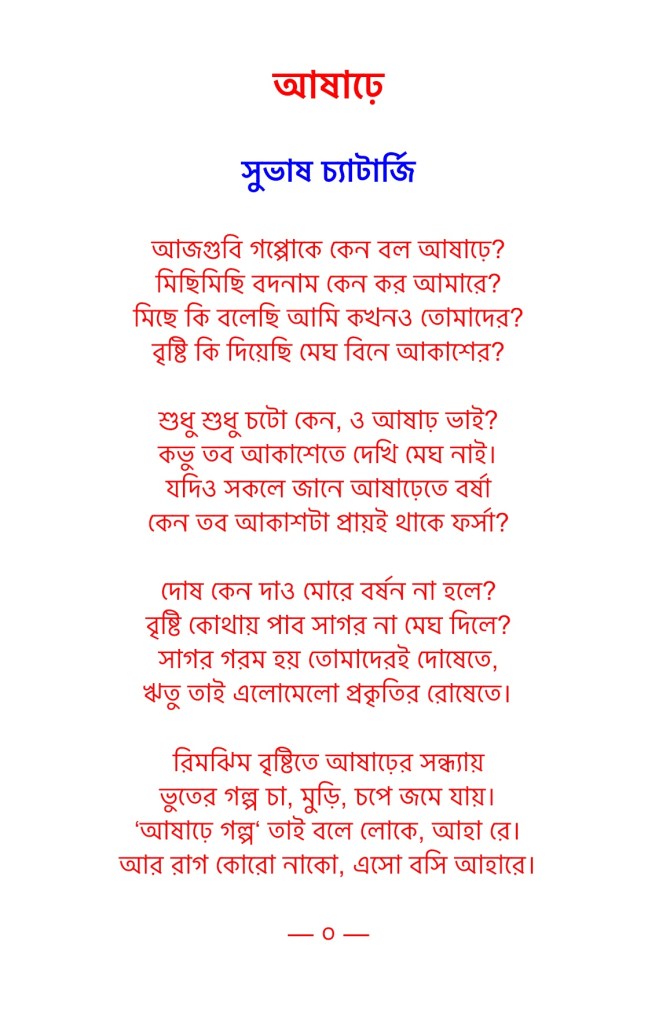
P8
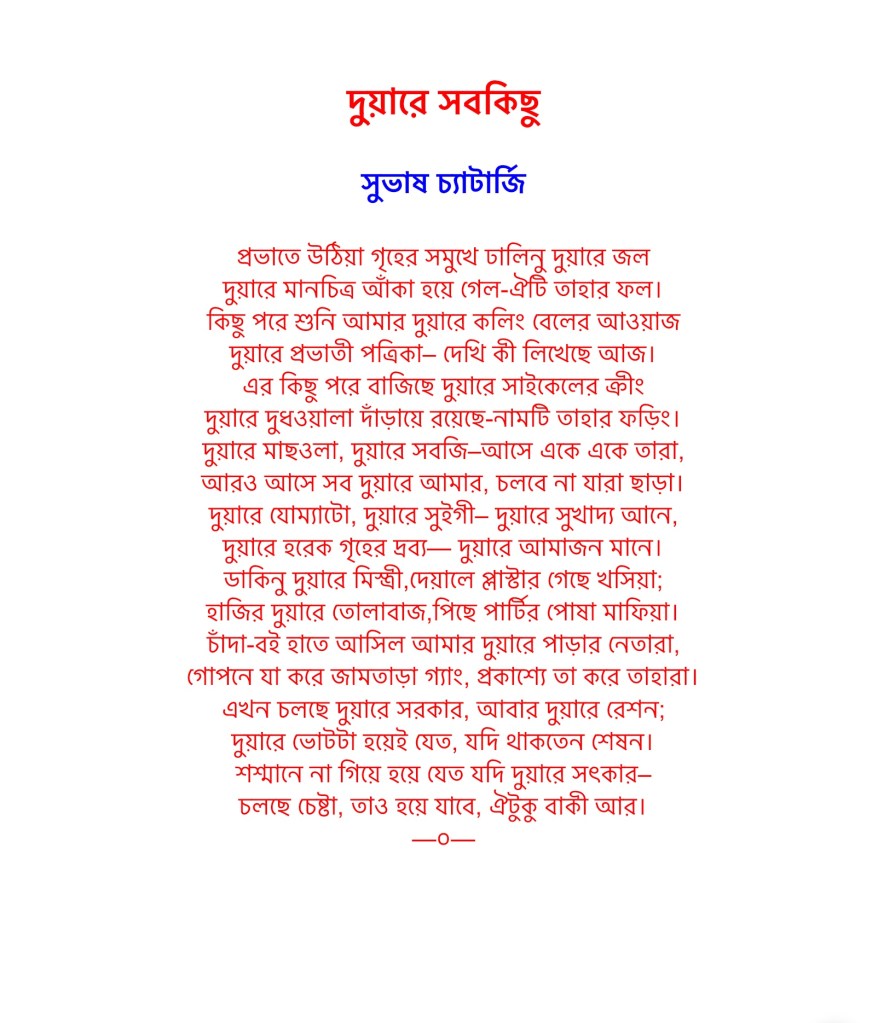
P9
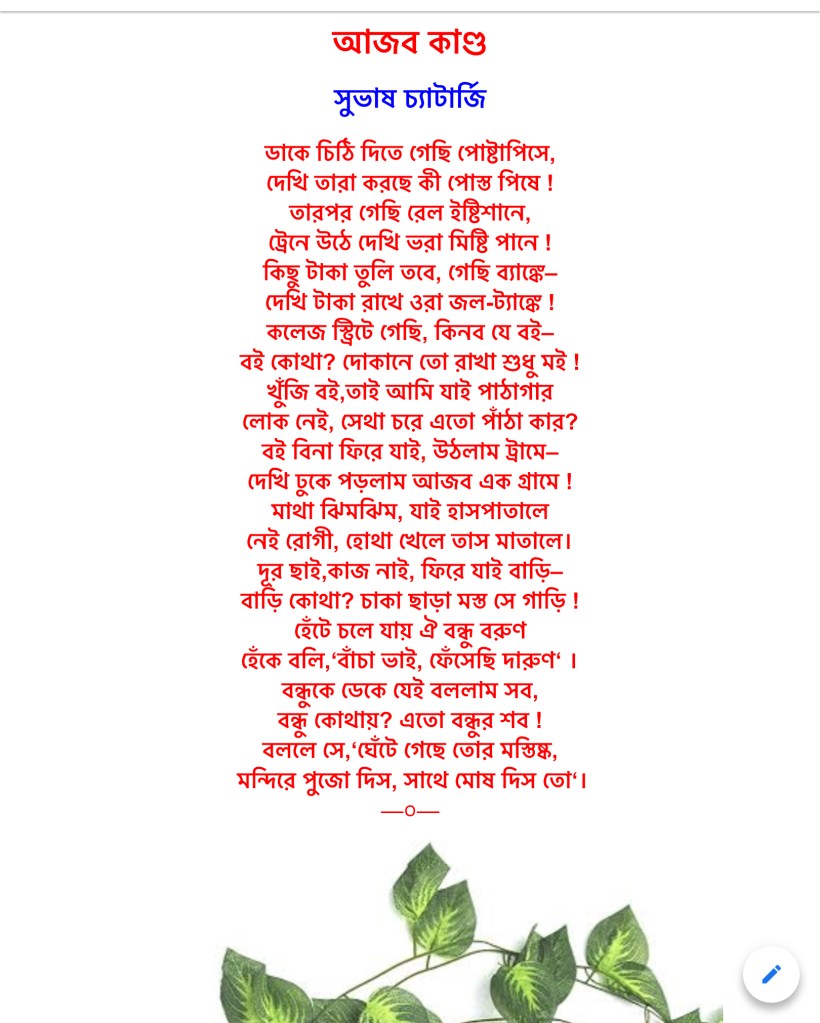
P10

P11
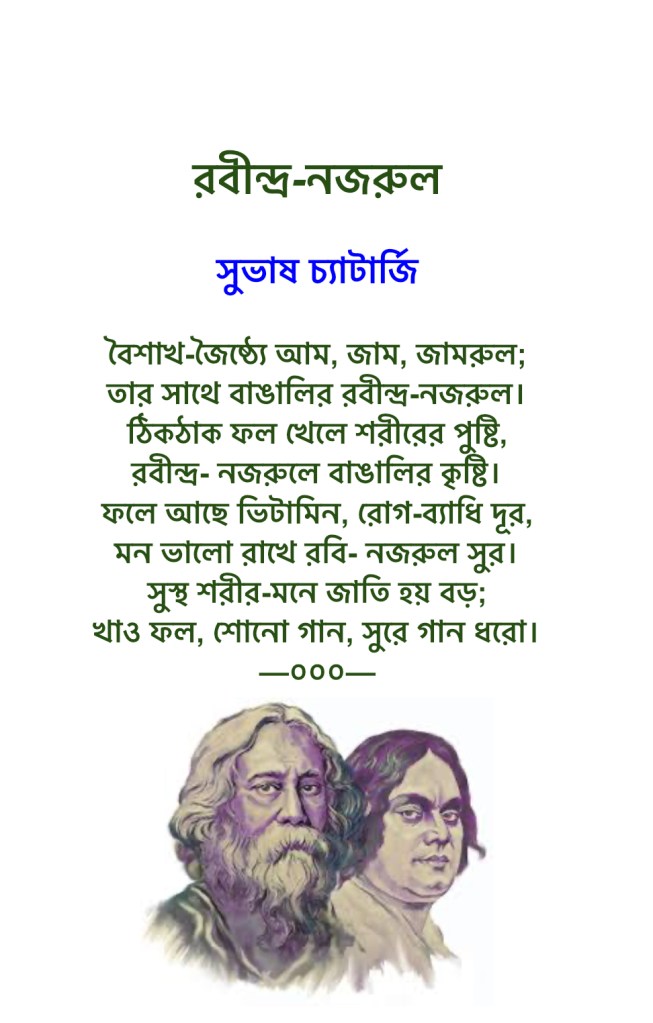
P12

P13

P14
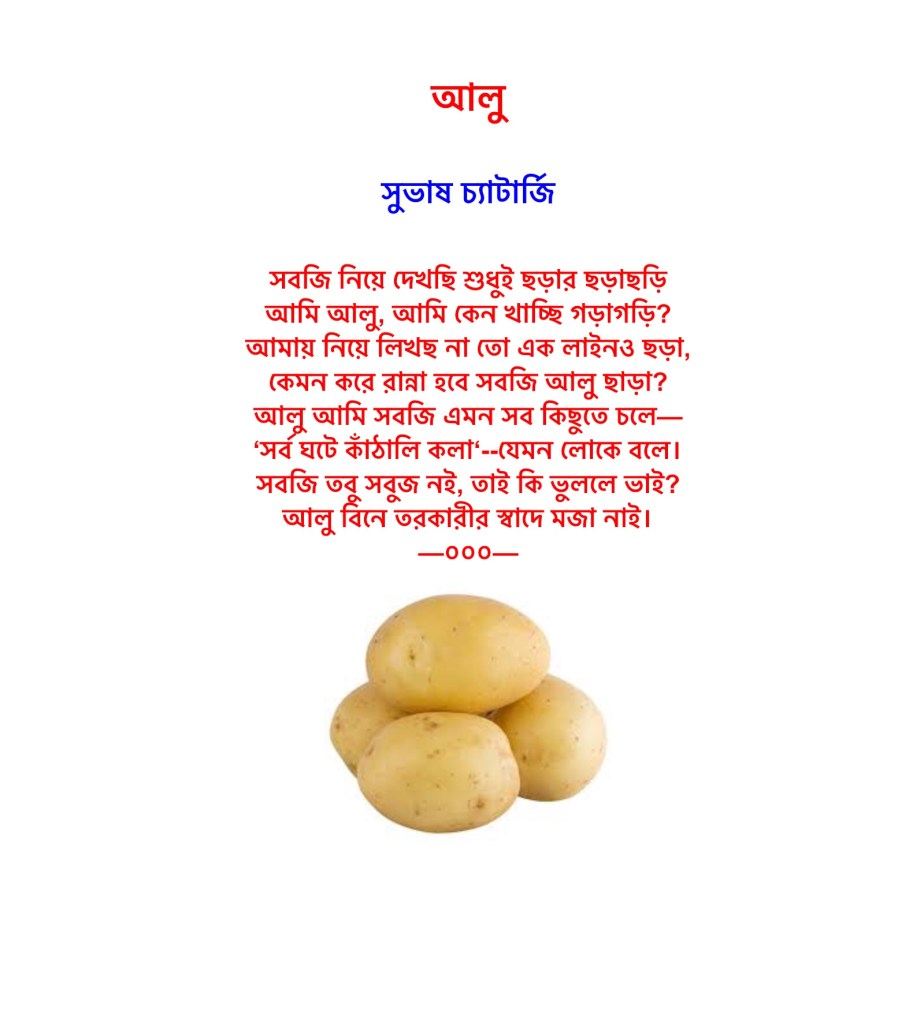
P15

P16
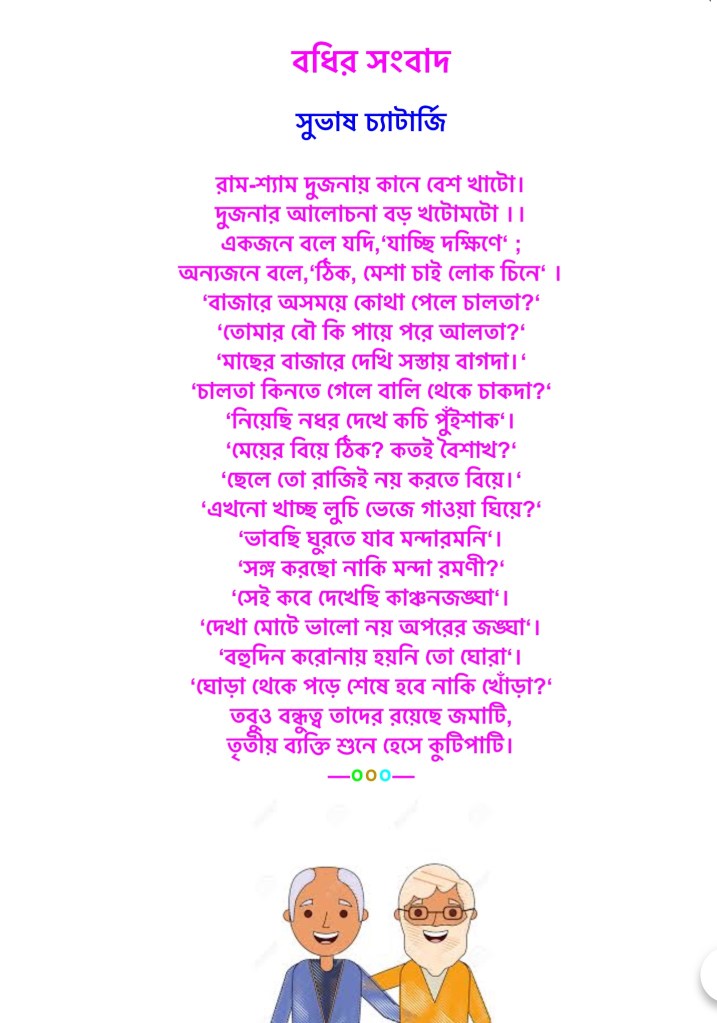
P17
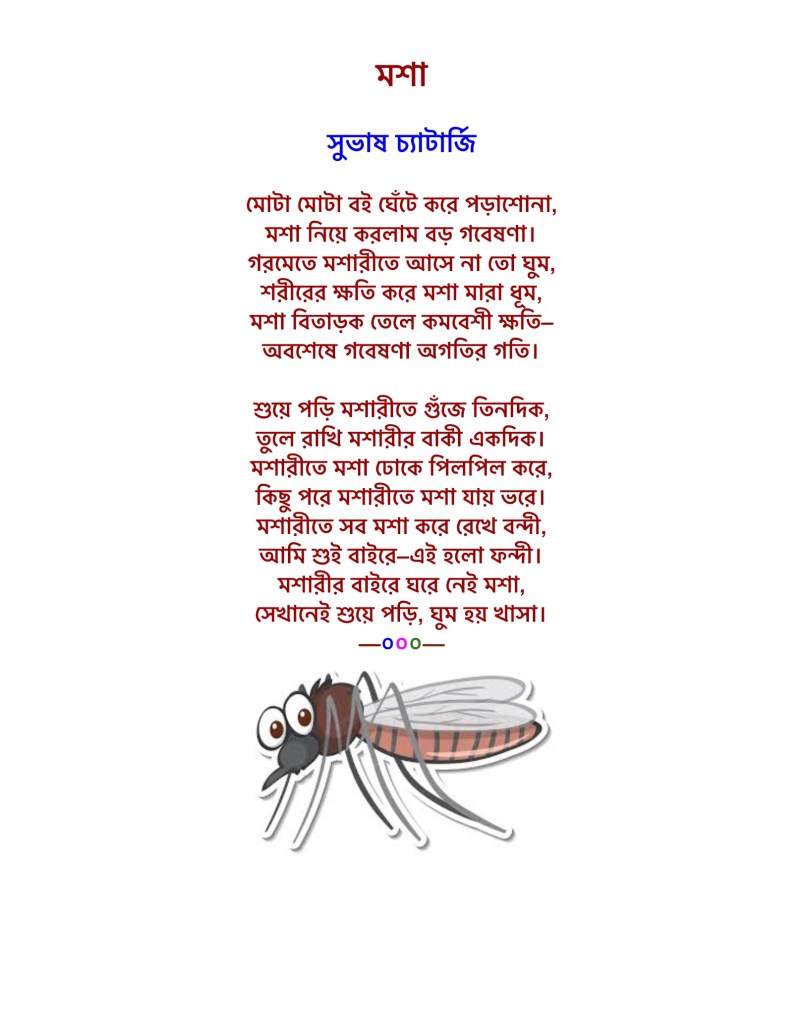
P18

P19

P20

P21
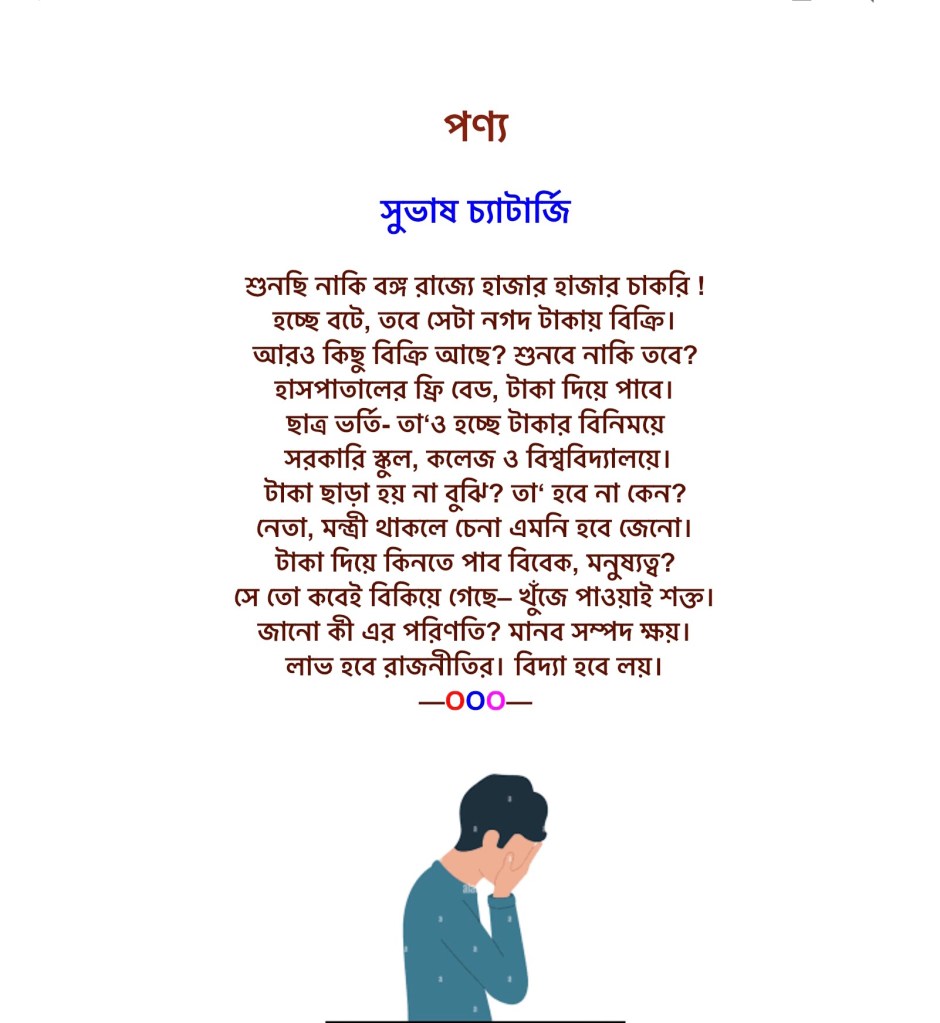
https://banglarpata.xyz/home/my-pages%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%be/এরকম আরও অনেক লেখা পড়তে My Pages~~ আমার পাতা দেখুন।
P22 কুকুর সুভাষ চ্যাটার্জি পূজোর দিনে মণ্ডপেতে দেখছে সবাই ঠাকুর, ভীড়ের মাঝে পথ হারিয়ে ঢুকল একটা কুকুর– লাঠি হাতে করল তাড়া পাহারাদার তাকে, ভীত কুকুর দৌড়ে এল দেখে আমাকে। থরথর কাঁপছে শরীর, চাইছে আশ্রয়; কোলে তুলে নিলাম তাকে করতে নির্ভয়। বাড়ি এনে দিলাম তাকে খাবার অল্প কিছু, খুশী হয়ে সারা বাড়ি ঘুরল আমার পিছু। পথ ভুলে সে এসেছিল, নাম হলো তাই ভোলা; বুঝতো ভোলা সব কিছুই, হলেও অবলা। কালীপুজোর বিসর্জনে আওয়াজ ভীষণ ভারী– বোম,বাজনা, ডিজে নিয়ে চলছে তাদের গাড়ি। সেই শব্দে অসুস্থ মা কষ্ট পাচ্ছে ঘরে, শব্দ কম করতে তাদের বলি করজোড়ে। ক্ষিপ্ত নেতা, হাতে পিস্তল ঢুকল আঙিনায়; হুমকি দিল,‘‘দেখে নেব,আয় বেরিয়ে আয়‘‘। ভীত আমি– লুকাই ছাদে, ভোলা আমার পিছে– উঁকি দিয়ে দেখছি দুজন, হচ্ছে কি সব নীচে। নেতার দল ঠেলছে দরজা ঢুকতে ঘরের ভেতর, দেখেই ভোলা দিল ঝাঁপ নেতার গায়ের উপর। নেতার টুঁটি ধরল ভোলা কামড়ে সজোরে, বাঁচতে নেতা করল গুলি ভোলার উপরে। ভাগলো সবাই ভয়ের চোটে, রইল পড়ে ভোলা, রক্তে ভাসল ভোলার শরীর,চোখ দুটো তার খোলা। আমায় দেখে দু‘ ফোঁটা জল পড়ল দু‘ চোখ বেয়ে, আমায় ঋণী করল ভোলা নিজের জীবন দিয়ে। —০০০—

P34

S3
ব্রহ্মচেতনা কী?
সুভাষ চ্যাটার্জি
আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি নিজেকে অর্থাৎ, নিজের শরীর,মন, সত্ত্বাকে।নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও প্রয়োজনে ঝগড়া করি। আবার প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদের সময় পরিবারের সব সদস্য এক হয়ে লড়াই করি। তখন আমি আর কেবল আমি থাকিনা, পরিবারের একজন হয়ে যাই। অন্য পাড়ার সঙ্গে কোন বিষয়ে স্বার্থের সংঘাত ঘটলে তখন আবার সেই প্রতিবেশীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে বেপাড়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। তখন আমি পাড়ার লোক। এই ভাবে নিজের আমিত্ব ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। যখন কোন ফুটবল খেলা দেখতে যাই, তখন বেপাড়ার যে লোকগুলোর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিলাম, তারা যদি আমার দলের সমর্থক হয়, তবে তাদের সাথেও একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করি। তখন তো আমি আর কেবল পাড়ার লোক নই, দলের সমর্থক। দেশ যদি বহিঃশত্রুর আক্রমনের শিকার হয়, তবে আমরা এক জাতি এক প্রাণ হয়ে সকল প্রতিবেশী, সব ফুটবল দলের সমর্থক, সব ধর্ম, ভাষার লোকেরা নিজেদের বিবাদ সরিয়ে রেখে এক যোগে একাত্ম হয়ে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। তখন আমার একমাত্র পরিচয় আমি দেশবাসী। আবার করোনার মতো মরণব্যাধির জীবানুর বিরুদ্ধে লড়াইতে সব দেশ যখন একজোট হয়ে যায়, তখন আমরা প্রত্যেকে বিশ্বমানবতার অংশ হয়ে যাই। এই ভাবে আমিত্ব যতই বিস্তার লাভ করতে থাকে, মনের মধ্যে অহং বোধ ততই লঘু হতে থাকে।
নিজের সত্ত্বার বিস্তার লাভ কিভাবে ঘটে, সেটা বোঝাতেই উপরের অংশের অবতারনা।
কিন্তু এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি করে প্রতিপক্ষ থাকছে। সেটা কখনো পরিবারের সদস্যরা, কখনো প্রতিবেশী বা অন্য পাড়ার লোক, অন্য দলের সমর্থক বা প্রতিবেশী দেশ অথবা মারণব্যাধি ইত্যাদি। কিন্তু পরিবার, পাড়া, দেশ, এমনকী বিশ্বমানবতা বা জীবকুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে যদি নিজেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশ হিসেবে কল্পনা করি, তবে আমার আর কোনো প্রতিপক্ষ থাকছে না। আমি তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি অনু পরমানুর একটি অংশ, আমার সত্ত্বা তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিলীন। আমি তখন সম্পূর্ণ আমিত্বহীন। এই ভাবনাটা মুখে বলা নয়, সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে হৃদয়ের গভীরে উপলব্ধি করাকেই বলে, ব্রহ্মচেতনা বা Cosmic Consciousness.
ব্রহ্মচেতনা কবিতার মধ্যে হৃদয়ের গভীরে এই চেতনার উপলব্ধির দুর্লভ মুহূর্তের আনন্দময় অনুভূতিটুকু বর্ণনা করা আছে।
S4
কিভাবে ব্রহ্মচেতনা উপলব্ধি করা যায়?
সুভাষ চ্যাটার্জি
ধ্যানের মাধ্যমে ব্রহ্মচেতনা উপলব্ধি করার জন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে মঠ বা আশ্রমে গিয়ে থাকার দরকার হয় না। বস্তুতঃ, মঠ বা আশ্রম একটা বৃহত্তর সংসার, যেখানে সদস্য সংখ্যা সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর তুলনায় অনেক বেশী। মঠাধ্যক্ষ ও অন্যান্যদের ব্যস্ত থাকতে হয়, মঠের খরচ চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তদারকিতে, দর্শনার্থী সামলাতে, দীক্ষা দান করতে ও দৈনন্দিন চাল, ডাল,সব্জি ইত্যাদি সংগ্রহ ,রন্ধন এবং সর্বোপরি সবকিছুর হিসাব রক্ষণ করতে। একজন গৃহীর তুলনায় কর্মব্যস্ততা কিছু কম নয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম, গৌতম বুদ্ধের পত্নী তাঁর সঙ্গে মঠে দেখা করতে এসে বলেছিলেন,‘‘ এত লোকজন পরিবৃত হয়েই যদি থাকবে, তবে রাজপ্রাসাদ কী দোষ করল?‘‘
সুতরাং, নিজ গৃহেই উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে সেখানে এই সাধনা করা যায়। উপযুক্ত পরিবেশ বলতে, চাই একটা ঘর যার দরজা,জানালা সব বন্ধ করে দিলে বাইরের কোলাহল আটকানো যায়। প্রয়োজনে মোটা পর্দা লাগানো যেতে পারে। ঘর মশাহীন হবে ও সাধনার সময় দ্বিতীয় ব্যক্তির আনাগোনা চলবে না।
নিজের সুবিধা মতো বসার জায়গা লাগবে।আসন বা হাতলওয়ালা চেয়ার দুই চলবে। প্লাস্টিক চেয়ার না। অতিরিক্ত নরম গদি নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অন্ততঃ আধ ঘন্টা বসলে শরীরের কোনো কষ্ট না হয়। হাঁটু মুড়ে আসনে বসবেন না পা টান করে চেয়ারে বসবেন, সেটা নিজের সুবিধা মতো ঠিক করতে হবে।পিঠ টান করে পেছনে সাপোর্ট রাখতে পারেন।
ঘরে হাল্কা সুগন্ধি রাখুন।কৃত্রিম গন্ধ চলবে না। ফুলদানিতে গোলাপ জাতীয় ফুল চলবে। চন্দন, অগুরু স্প্রে করা যায়। কিন্তু ধূপকাঠি বর্জন করুন, শ্বাসকষ্ট হতে পারে। উগ্র গন্ধ একদম নয়। যে গন্ধ ব্যবহার করবেন, তা অন্য সময় করবেন না, তাহলে শরীর ও মন কন্ডিশনড হবে এবং এই গন্ধ পাওয়া মাত্রই মন ধ্যানের জন্য তৈরি হয়ে যাবে। ঘরে হাল্কা নাইট ল্যাম্পের আলো থাকবে।
ধ্যানের উপযুক্ত সময় দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণ, অর্থাৎ, ঊষাকালে ও সন্ধ্যায়। ঊষার সময় খালিপেটে করতে পারেন, কিন্তু সন্ধ্যায় ভরাপেট বা খালিপেটে নয়। হালকা খাবার খেতে হবে।
ধ্যানযোগের মূল আছে পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে। এই যোগের আটটি পর্যায়:- যম, নিয়ম, আসন, প্রানায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা , ধ্যান, সমাধি। প্রথম চারটি পর্যায় শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে শরীর সুস্থ না থাকলে মন একাগ্র করা কঠিন হবে।
প্রথম পর্যায়ে যম অর্থ সংযম।আহার বিহারে সংযম না থাকলে শরীরে সমস্যা হবে। অতিরিক্ত ভোজনে হজমের সমস্যা হলে স্থির চিত্ত হওয়া কষ্টকর।
নিয়ম অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে আহার, নিদ্রা ইত্যাদি। আহারে অনিয়ম শরীরে অসুবিধা সৃষ্টি করে। রাত্রি জাগরণের ফলে ধ্যানের সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।
আসন ও প্রানায়াম নিজের শরীরের প্রয়োজন বুঝে করবেন। এই স্বল্প পরিসরে এখানে বিশদে বলা সম্ভব নয় । কিছু কিছু আসন, প্রানায়াম মনকে শান্ত করতেও সাহায্য করে।
পঞ্চম পর্যায় প্রত্যাহার থেকে আমি বিশদে আলোচনা করব।মনকে একাগ্র করার জন্য
ওঁ জপ করতে পারেন। ওঁ জপে আপত্তি থাকলে ক, খ,গ, ঘ এই চারটি কণ্ঠ্য বর্ণের যে কোনোটি জপ করতে পারেন।ঘ বর্ণ এর মধ্যে সব থেকে গম্ভীর হওয়ায় জপ করা ভালো। জপ অর্থ উচ্চারণ নয়।নিম্ন কম্পাঙ্কের ধ্বনিতে যে গম্ভীর নাদের সৃষ্টি হয়, তাকে সমস্ত শরীর মন দিয়ে অনুভব করা।ঢাকে একবার কাঠি মারার ঠিক পরেই যে গুরুগম্ভীর গুরুগুরু শব্দের কম্পন সৃষ্টি হয়,অনেকটা সেই রকম। নাভিমূল থেকে ওঁ উচ্চারিত হলে এই ধ্বনি পাওয়া যায়। এই ধ্বনিকে জপ করতে হবে স্থির ভাবে বসে।
জোর করে পড়তে বসালে শিশু যেমন সুযোগ পেলেই পড়া ছেড়ে খেলতে শুরু করে, মনও প্রথম দিকে জপের সময় শিশুর মত জপ ছেড়ে মাঝে মাঝেই পার্থিব চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে।এতে উদ্বেগের কিছু নেই।খেয়াল হওয়া মাত্র আবার জপ শুরু করতে হবে। ক্রমশঃ বাইরের চিন্তা কমতে থাকবে এবং মন বাধ্য ছেলের মতো জপে নিমগ্ন হবে।
প্রত্যাহার (withdrawal) অর্থ বাহ্যিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। বাহ্যিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় চক্ষু, কর্ন,নাসিকা, জিহ্বা,ত্বক— এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। চোখের পাতা বন্ধ করলে তার কাজ বন্ধ। ঘরে শব্দ যত কম আসে ততই ভালো, তাতে কর্নের কাজ কমবে। নাসিকা, জিহ্বার কাজও কম বা নেই। সমস্যা হবে ত্বক নিয়ে।মশার তেল ঘরে রাখতে হবে।
তবুও একাগ্রতা যত বৃদ্ধি পায়, ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা তত বৃদ্ধি পায়।একে বলা হয় state of exalted sensibility. ফলে বিনা কারণে নাকে,ঘাড়ে, হাতে ,পায়ে মশা কামড়ের মতো তীব্র চুলকানোর অনুভূতি হতে পারে। সামান্য শব্দ জপে মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এগুলো উপেক্ষা করে ধ্যান করে যেতে হবে।তবেই প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হবে।
প্রত্যাহারের গভীর স্তরে নিজে থেকে আসে ধারণা পর্যায়। আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি, এই পর্যায়ে সেই রকম বন্ধ চোখের সামনে নানা ছবি আসতে থাকে।অনেক পুরনো ঘটনা, জীবিত ও মৃত মানুষ সবই সিনেমার মতো চলতে থাকে। ভয়ের কিছু নেই।মনের ভেতরে চাপা পড়ে থাকা নানা চিন্তা, আবেগ — এগুলো সব বেরিয়ে এসে এইভাবে মনকে চাপমুক্ত করে। ফলে মন ক্রমশঃ গভীর প্রশান্তির জগতে প্রবেশ করে। তবে একদিনে না, আস্তে আস্তে ঘটে। ধীরে ধীরে ছবি আসা কমতে থাকে ও মন শান্ত হতে থাকে। জিহ্বাতে মিস্টি স্বাদ অনুভূত হতে পারে।হাত ,পা, বা শরীরের অন্য অংশের অস্তিত্ব বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। অর্থাৎ, হাত চেয়ারের হাতলের উপর না কোলের ওপর, তা বুঝতে পারবেন না। পায়ের হাঁটু টান করা না ভাঁজ করা, সেই অনুভূতি থাকবে না। প্রত্যাহার ও ধারণা এইভাবে সম্পূর্ণ হয়।
এবার ধ্যান (Transcendental meditation) পর্যায়। জাগ্রত অবস্থায় মন চিন্তাহীন থাকতে পারে না। কিন্তু জপ করতে করতে মাঝে মাঝে দু‘একটি মুহূর্ত এমন পাবেন, যখন জপ হারিয়ে যাবে ও মাথায় অন্য কোন চিন্তাও আসবে না । মন তখন সম্পূর্ণ একটা নিস্তরঙ্গ পুকুরের মতো শান্ত, যেখানে কোন চিন্তার ঢেউ নেই। বন্ধ চোখের অন্ধকার সরিয়ে ফুটে উঠবে আলোর জ্যোতি। কয়েকটি মুহূর্ত অথবা কয়েক সেকেন্ড — তার মধ্যে মনের গভীরে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হয়ে যাবে। অদ্ভুত, অনির্বচনীয় অনুভূতি। এই সেই আমিত্বহীন সত্ত্বার অনুভব যা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ব্রহ্মচেতনার অপূর্ব স্বাদ এখানেই পাওয়া যায়।
বেশীক্ষণ স্থায়ী হলে যোগের অষ্টম বা শেষ পর্যায় সমাধি শুরু হয়। সমস্ত সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে ব্যস্ত থেকে এই পর্যায়ে পৌঁছানো যায় না।এরজন্য বাস্তব জীবনের সকল ক্রিয়াকাণ্ড থেকেও নিজেকে প্রত্যাহার করতে হবে।সমাধির অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাই, এই বিষয়ে আলোচনা করব না।
P35
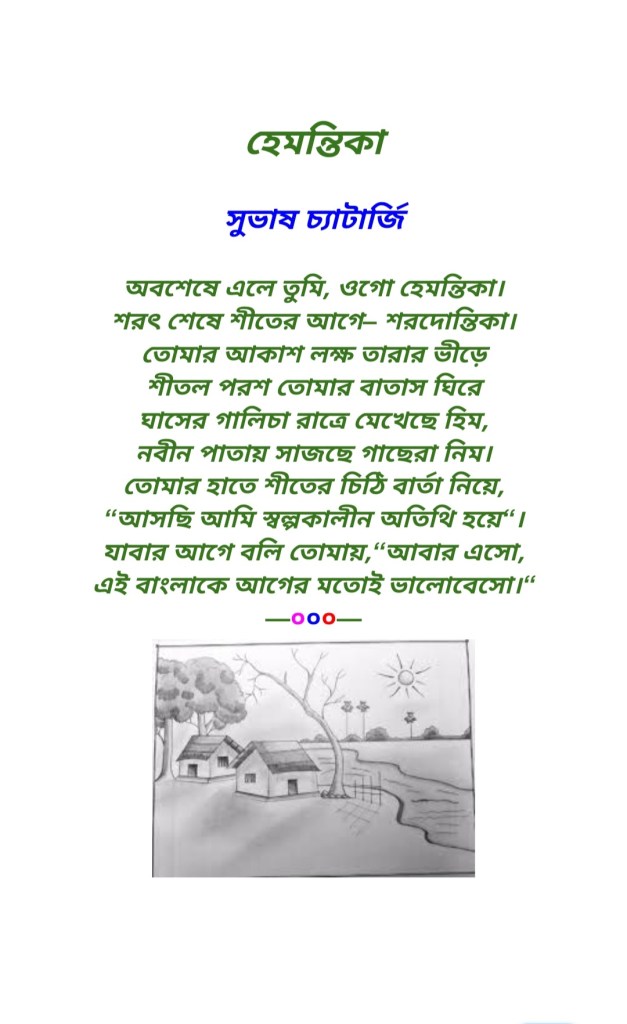
S7
সর্পদংশন
সুভাষ চ্যাটার্জি
তখন আমার কতই বা বয়স! ক্লাস ফোর কি ফাইভে পড়ি।থাকতাম গ্রামে।বাড়ির পাশে বিশাল পুকুর, কিন্তু তেমন গভীর নয়। গরমের ছুটিতে স্নানের সময় পুকুরে হুটোপুটি করতে করতে ঘণ্টা পার হয়ে যেত। আমার সঙ্গী ছিল বছর তিনেকের বড় দাদা, দেড়-দু বছরের ছোট বোন, পাড়ার কিছু সমবয়সী ছেলে, তাদের আর আমাদের মায়েরা।মায়েদের মূল কাজ ছিল, নির্দিষ্ট সময়ের পর জল থেকে আমাদের উঠিয়ে আনা।
জলে নামবার মুখে অল্প জলে অর্ধেক ডোবানো একটা মাঝারি মাপের সিমেন্টের চাঁই, যেখানে মেয়েরা জামাকাপড় কাচে।তার পাশ দিয়ে স্নানের পর উঠে আসছি, হঠাৎ গোড়ালির কিছুটা উপরে দংশনের তীব্র জ্বালা অনুভব করলাম। আতঙ্কে পা-টাকে সামনের দিকে খুব জোরে এক ঝটকা দিলাম।পা-টাকে বেড় দিয়ে জড়িয়ে থাকা একটা সাপ প্রবল ঝটকায় সামনের দিকে ছিটকে পড়ল।তারপর সবেগে পাড়ের জঙ্গলে ঢুকে গেল। আমার পায়ে সাপের বসে যাওয়া দাঁত ঝটকার জন্য পায়ের চারপাশে একটা বৃত্তাকার রক্তের রেখার সৃষ্টি করেছে। ভীষণ ভয়ে আমার পা থরথর করে কাঁপতে লাগলো।
স্কুলে বিজ্ঞান ক্লাসে মাস্টারমশাই পড়িয়েছেন, সাপে কামড়ালে দংশন স্থানের উপরে শক্ত করে বাঁধন দিতে হবে। আমি সঙ্গে থাকা গামছা দিয়ে বাঁধন দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমার হাত ও সমস্ত শরীর ততক্ষণে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।মা তখন দাদাকে বাড়িতে পাঠাল বাবাকে খবর দিতে।
স্নানঘাটের কাছেই হাসপাতালের বহির্বিভাগে বাবা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন।তখন সবে রোগীর ভিড় শেষ হয়েছে। ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, নার্স মিলে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সেখানে আমরা মূর্তিমান রসভঙ্গ রূপে আবির্ভূত হলাম। বাবা সব ঘটনা ডাক্তারবাবুকে জানালেন। ডাক্তার আমার ভেজা হাফপ্যান্ট,খালি গায়ের দিকে এক নজর দেখে নিয়ে নিদান দিলেন, “এইভাবে বাঁধন দেয়? এই পেসেন্টকে আমি বাঁচাতে পারব না; নিয়ে যান ওকে এখান থেকে।” বাবা বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।
আমাদের ছোট্ট গ্রামে অল্প দূরে বড়াল পাড়া। সেখানকার শীতল বড়াল লোকের বাড়িতে পূজো করেন। আমাদের বাড়িতেও পূজো করতে আসেন।ওঝার কাজও করেন। বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। উনি ভালো করে ক্ষতস্থান ও তার আশপাশ পরীক্ষা করে বললেন, “খুব বেশি বিষ ঢালতে পারেনি। সম্ভবতঃ জলঢোঁড়া বা ঐ জাতীয় কোন অল্প বিষের সাপ হবে।হয় তো লেজে পা পড়েছিল অথবা মাছ ভেবে কামড়ে থাকবে।” তারপর ঠাকুরের আসন থেকে একটা সিঁদুরের কৌটো নিয়ে এলেন।তার ভেতর থেকে একটা বিষ পাথর বের করে সেটা ক্ষতস্থানে চেপে ধরলেন।একটু পরে ছেড়ে দিলেও পাথরটা ক্ষতস্থানে ঝুলেই থাকল। উনি তখন কয়েক গাছা চুল নিয়ে বাঁধনের নীচ থেকে বিষ পাথর পর্যন্ত টেনে টেনে ঘষতে থাকলেন। মিনিট পনেরো পরে বিষ পাথর ক্ষতস্থান থেকে খুলে পড়ে গেল। উনি একটা বাটিতে কিছুটা দুধ নিয়ে তার মধ্যে বিষ পাথরটা দিয়ে দিলেন। একটু পরে দুধটা নীল রং হয়ে গেল। আমাকে বললেন, “বাঁধন খুলে বাড়ি চলে যাও; আর কোন ভয় নেই।” বাবাকে বললেন, “ঘরে ফিরে ওকে গরম দুধ দেবেন। আর দুপুরে ঘুমাতে দেবেন না।”
বাড়িতে মা আমাকে গরম দুধ আর সুজি দিলেন।খাওয়ার পর ছোট বোন আর দাদাকে বললেন আমার সঙ্গে গল্প করে আমাকে জাগিয়ে রাখতে। কিন্তু আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না; কারণ শরীরের মধ্যে একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে।গায়ে একটা শীত শীত ভাব। ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে আসছে।সাপে কাটলে কি এমন হয়? কি করে জানব? বিজ্ঞান বইতে তো লেখা নেই। আর আমার চেনা যাদের সাপে কেটেছে, তাদের কেউ আমাকে বলার জন্য বেঁচে নেই। আমার মনে হল, হয়তো আমার শরীরে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। মনে পড়ল, স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক মশায় বলেছিলেন, “সাপে কামড়ালে ডাক্তার দেখাবে; ওঝার কাছে গেলে বিপদ বাড়বে, কারণ ঝাড়-ফুঁকে বিষ নামে না।” কিন্তু বাবা তো আমাকে হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। ডাক্তার কিছু করল না। ওঝা যদি বিষ নামাতে না পেরে থাকে, তবে বাবার আর কি করার আছে? আমার শরীরে অসুবিধের কথা বাবা-মাকে বললে শুধুই ওদের মনোকষ্ট বাড়বে।কাজেই ঠিক করলাম, কাউকে কিছু বলব না।
হাতে সময় খুব কম; কাল সকালের সূর্য দেখব কিনা জানিনা। এখন আমার যা করার আছে, তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমার ঘুড়ি, লাটাই, হাতলাট্টু, কাচের গুলি, লাট্টু, লেত্তি– এগুলোর উপর দাদার খুব লোভ; ওকে ডেকে এগুলো সব দিয়ে দিলাম।ও অবাক হলেও সব নিয়ে নিল। ছোট বোন বলল, “দাদা, আমাকে কিছু দিবি না?” আমার সংগৃহীত সব প্রিয় জিনিষগুলো আর রেখে কী হবে, যখন আমিই থাকব না? প্লাস্টিকের পুতুলগুলো, প্লাস্টিকের হাতি, ঘোড়া, গরু সব বোনকে দিয়ে দিলাম। মামা আমাকে তারকেশ্বরের মেলা থেকে একটা নম্বর লক দেওয়া ছোট টিনের সিন্দুক কিনে দিয়েছিলেন, যেটাতে আমি পয়সা জমাতাম।দাদার অনেক দিনের নজর ওটার উপর। সেটা ওকে দিয়ে দিলাম।ভেতরে জমানো তামার ফুটো পয়সা, দু‘ পয়সা, এক আনা, দু‘ আনা, চকচকে নতুন তামার এক নয়া পয়সা, ঢেউ খেলানো দুই নয়া, চৌকো পাঁচ নয়া, দশ নয়া সব বোনকে দিলাম। এতদিন প্রাণে ধরে কাউকে দিতে পারি নি। আজ দিতে পেরে খুব হালকা লাগছে।
আমার পঁচিশ-ত্রিশটা গল্পের বই ছিল। কোনোকালে এগুলো আমার থেকে বয়সে অনেক বড় দাদা দিদিদের ছিল।আমি পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে সংগ্রহ করে শখের লাইব্রেরী বানিয়েছিলাম। রূপকথার গল্প, নীহার রঞ্জন গুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য-রোমাঞ্চ, পুরানো শুকতারা, শিশু সওগাত, মাসিক বসুমতী, মনিভদ্র রাজকন্যা আরও কত বই ! এগুলো আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। স্কুলের লাইব্রেরী বইয়ের প্রথম পাতায় পাঠাগারের সীলমোহর থাকে দেখে আমার বইগুলোতেও ছাপ লাগিয়েছিলাম। পুরনো একটা টিনের জ্যামিতি বাক্সের উপর অর্ধ উদিত সূর্যের লোগো, তার সাথে ‘সানরাইজ‘ লেখা খোদাই করা ছিল। সেটাকে আমার লাইব্রেরীর সীলমোহর বানিয়ে পেনসিলের পেছন দিয়ে ঘসে বইগুলোর পাতায় ছাপ মেরেছিলাম।আর লাইব্রেরীর নাম রেখেছিলাম ‘সূর্যোদয় পাঠাগার’ । একই বই বারবার পড়তাম, পাতার গন্ধ শুঁকতাম; দাদা, বোনকে পড়তে দিতাম। এদিন সব মায়া ত্যাগ করলাম। বইগুলোর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে বোন আর দাদাকে বললাম, “তোদের যার যেটা ইচ্ছে, নিয়ে নে।”
এখন আমি মুক্ত। মনের মধ্যে খুব হালকা লাগছে, আনন্দও হচ্ছে। কিন্তু শরীরের কষ্টটা আরও বেড়েছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। আর বসে থাকতে পারছি না।মেঝেয় পাতা মাদুরের উপর শুয়ে পড়লাম।তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয় হয়।বোন আর দাদা কিছু একটা আঁচ করে মাকে ডাকতে থাকল।মা তাড়াতাড়ি এসে গায়ে হাত দিয়ে বললেন, “ওর তো ধূম জ্বর; গা পুড়ে যাচ্ছে।” তারপর বালতি করে জল এনে কপালে জলপট্টি দিতে থাকলেন। কি জানি, বিষের প্রভাবে কি জ্বরও আসে? মা বললেন, “জ্বরের আর দোষ কী? ভিজে গায়ে, মাথায় অতক্ষণ খালি গায়ে থাকা– তার উপর দুপুর রোদে ঘোরাও তো কম হয় নি।”
জলপট্টিতে একটু আরাম হলো। এক গ্লাস দুধ সাবু খেয়ে মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম, মরলে এই ভাবেই যেন মায়ের কোলে শুয়ে মরি !
চোখের সামনে আবছা একটা অবয়ব। যমদূত, নাকি যমরাজ নিজে? গল্পের বইতে পড়েছি, ওরা নাকি মৃত্যুর সময় হাজির হয়। আসতে আসতে চেহারাটা স্পষ্ট হোল। বিজ্ঞান শিক্ষক আর ওঝা মশাই মিলে মিশে একাকার– এক হাতে চক-ডাস্টার আর অন্য হাতে বিষ পাথর।বলার চেষ্টা করলাম, “স্যার, আমি তো বাঁধন দিয়েছিলাম, ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলাম।” কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরলো না।
পূর্ব দিকের খোলা জানালা দিয়ে সকালের ঝলমলে সোনালী রোদ চোখের উপর পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। গতকালের ঘটনা সব মনে পড়ে গেল। কী আশ্চর্য ! আমি বেঁচে আছি ! মনটা এক অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। না, আমার এতদিনের জমানো সম্পদ সব বিলিয়ে দেওয়ার জন্যও মনের কোণে কোথাও এতটুকু দুঃখ আর জমে নেই। পৃথিবীটা যেন এক রাতের মধ্যেই আরও সুন্দর হয়ে সেজে উঠেছে।
—০০০—
S8
না-মানুষী কথা
সুভাষ চ্যাটার্জি
ঘটনাটা আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা। বন্ধুটি মীরাক্কেলের প্রথম দিকের কোনো এক পর্বের প্রথম স্থানাধিকারী। কিন্তু, তার কৃতিত্ব সে নিজেকে পুরোপুরি দিতে রাজী নয়।তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সে এই ঘটনার কথা বলেছিল। আমি তার বয়ানেই পুরো ঘটনাটা তুলে ধরছি।
বন্ধুর নাম বাসু। ছোট মফস্বল শহরে পূজোর সময় পাড়ায় পাড়ায় হাস্যকৌতুকের অনুষ্ঠান করে বেশ নাম করেছিল। মানুষকে হাসানোর জন্য তার নামটা বাসুবাবুর থেকে হাসুবাবু চালু হয়ে গিয়েছিল।বাসুরও সেটা বেশ পছন্দ হয়েছিল।টিভি সিরিয়ালে তার সাফল্যের পর ছোট শহরে তাকে নিয়ে বেশ হইচই পড়ে গিয়েছিল। তার সাফল্য উদযাপনের জন্য তাকে একদিন আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে বেশ জমিয়ে গল্প করছি। তখনই সে তার গল্প বা গুল্প শুরু করল।
‘‘তোরা আমার সাফল্য নিয়ে এত হইচই করছিস! আমি কিন্তু এই কৃতিত্বের একশো ভাগ দাবিদার নই। গ্র্যান্ড ফিনালের কদিন আগে আমার সঙ্গে যা ঘটেছিল, তা যদি না হোত তবে হয়তো সব কিছু অন্যরকম হোত।”
গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি বেশ গুছিয়ে বসে বললাম,‘‘শুরু কর, শেষ পর্যন্ত না শুনে ছাড়ছি না।” বাড়ির সকলে গুটি গুটি পায়ে এসে চারপাশে ঘিরে বসল।
বাসু আবার শুরু করল,‘‘ টিভির অনুষ্ঠানের শুটিং শেষ হতে বেশ রাত হতো।লাস্ট ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরতাম। স্টেশন থেকে আমার বাড়ি একদম কম দূরত্বে নয়, সেটা তুই জানিস। অন্য সময় পায়ে হেঁটে এলেও বেশি রাতে রিক্সায় ফিরতাম। কিন্তু সেদিন মাঝপথে রিক্সার চাকা পাংচার হওয়ায় রিক্সাওয়ালা বলে দিল,‘‘বাবু, আজ আর যেতি পারব নি, এটুকু রাস্তা আপনাকে আজ একটু হেঁটে যেতি হবে।তবে রাস্তা ধরেই যান, লেকের ভেতর দিয়ে যাবেন নি।”
রিক্সাওয়ালা তো বলেই খালাস! এদিকে ট্রেন লেট থাকার জন্য আজ আমার এমনিতেই দেরী হয়েছে।তার উপর আবার এই বিপত্তি।খিদেও খুব পেয়েছে। লেকের ভিতরের রাস্তাটা অনেক শর্টকাট।তাই আমি ঠিক করলাম, লেকের পাঁচিলের ভেতরের রাস্তা ধরেই যাব। পাঁচিলের ভাঙা অংশ দিয়ে লেকের পাড়ের রাস্তায় পৌঁছে গেলাম।সেটা ধরে জোরে হাঁটতে থাকলাম। লেকের পাড়ে বিশাল বিশাল গাছ।আকাশে আধ-খাওয়া চাঁদ থাকলেও তার জ্যোৎস্না গাছের ডালপালা ভেদ করে পুরোপুরি রাস্তায় পড়ছে না; একটা মায়াময় আলোআঁধারি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। জোরে পা চালিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ সোঁ সোঁ করে জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল।আমাকে অবাক করে হাওয়া ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ঝড়ে পরিণত হলো।সেই ঝড়ের দাপটে আমাকে তুলে বটগাছের উপরে নিয়ে ফেললো।
হতচকিত হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, আমার চারপাশে অনেক গুলো ছায়ামূর্তি আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম,‘‘এই তোমরা কারা? আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছো?”
ওদের মধ্যে ষণ্ডা মতো একজন বললে,‘‘তোমার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আছে। তুমি মানুষদের নিয়ে হাস্যকৌতুক কর; এমনকি, জন্তু জানোয়ারদের নিয়েও কর। কিন্তু আমাদের নিয়ে কেন কর না? আমরা কি এতই অছেদ্দার পাত্র?”
আমি একটু ভয় পেয়ে সম্ভ্রম দেখিয়ে বললাম,‘‘ কিন্তু আমি তো জানিই না আপনারা কারা?”
আর একজন বললে,‘‘ আমরা তোমার ভবিষ্যৎ। তুমি মরলে আমাদের দলেই আসবে।”
আমি অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে বললাম,‘‘ ছি,ছি! আপনাদের নিয়ে কি রসিকতা করতে পারি? তাতে আপনাদের অসম্মান করা হবে। বরং, আপনারাই মীরাক্কেলের মতো একটা ভুতাক্কেল অনুষ্ঠান করুন না।”
এতক্ষণে আমি বুঝে ফেলেছি যে, আমি ভুতের পাল্লায় পড়েছি। আর ষণ্ডামার্কাটা ওদের রাজা; ব্রহ্মদত্যি গোছের কিছু একটা হবে। সে আমার কথায় খুশি হয়ে বললে,‘‘ খুব ভালো প্রস্তাব; কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানে অংশ নিলে বিচারক কে হবে? তুমি তাহলে বিচারক হও।”
আমি ততক্ষণে ভয় কাটিয়ে ফেলেছি। দেখলাম, এটা একটা সুযোগ। বললাম, ‘‘ আমি রাজি; কিন্তু আমি কী পাবো?”
ওদের রাজা বলল,‘‘ তোমাকে তিনটি বর দিচ্ছি। তুমি ইচ্ছে মতন বর চাইতে পার।”
আমার তখন গুপী গায়েন বাঘা বাইনের ভুতের রাজার কথা মনে পড়ে গেল। আর মীরাক্কেলের ফাইনালে যাওয়ার কথা তো সবসময় মাথায় ঘুরছে। তাই, অন্য বর না চেয়ে আমি বললাম,‘‘ মীরাক্কেলের ফাইনালে যেন যাইতে পারি – এক নম্বর, এক নম্বর। চ্যাম্পিয়ন যেন হইতে পারি– দুই নম্বর, দুই নম্বর। লাখ টাকা পুরস্কার পাইতে পারি– তিন নম্বর, তিন নম্বর।” ভুতের রাজা তখনই নাকী সুরে হেঁড়ে গলায় বলে উঠলো,‘‘ মঞ্জুর, মঞ্জুর।” সে কী আওয়াজ! মনে হলো, ফাটা ঢাকের সঙ্গে ফাটা কাঁসর বাজছে।
তারপর অনুষ্ঠান শুরু হলো; একে একে রাজামশাই ও অন্যরা অংশগ্রহণ করল। এবার বিচারক হিসেবে আমার ফল ঘোষণার পালা। আমার বুকটা দুরুদুরু করতে লাগলো। আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম, ‘‘রাজামশাইকেই বিচারে প্রথম করব।না হলে বর তো ফেরত নিয়ে নেবেনই, তাছাড়া আরও বড় বিপদে পড়তে পারি।তাই, রাজা মশাইকে প্রথম স্থানাধিকারী বলে ঘোষনা করলাম।তারপরই সাংঘাতিক এক কাণ্ড ঘটলো।
আমি তো আর জানতাম না যে, রাজামশাইয়ের একটি বিরোধী গোষ্ঠী আছে। তারা রে,রে, করে আমার দিকে তেড়ে এলো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে চ্যাংদোলা করে তুলে গাছের উপর থেকে সোজা নীচের দিকে ছুঁড়ে ফেললো।আমি আতঙ্কে চোখ বুঁজে ফেললাম; আর রাজামশায়ের সাহায্য চেয়ে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলাম,‘‘ বাঁচাও, বাঁচাও”। আর তারপরেই ধপাস করে নীচে আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।
কে যেন আমাকে সজোরে ধাক্কা মারছে।সভয়ে চোখ খুলে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আমার মা। কোনরকমে বললাম,‘‘আমি কোথায়? হাসপাতালে?” মা বলল,‘‘ বাড়িতে। ঘুমের মধ্যে খাট থেকে পড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছ। অত রাত পর্যন্ত মীরাক্কেল করে উল্টোপাল্টা চিন্তা করলে পেট গরম হয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে এই রকমই হয়।”
তারপর বাসু ওর মন্তব্য যোগ করল,‘‘ দেখ, এর পরেই শো-তে আমার চ্যাম্পিয়নশিপ। আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস, সামথিং, সামথিং, হ্যাপেনড ইন স্লিপিং। না হলে কি আর গরীবের ভাগ্যে প্রাইজের শিকে ছেঁড়ে?”
গল্পের এখানেই শেষ। আপনারাই ঠিক করুন, এটা ঘটনা না গুল্প।
—০০০—
S9
খরুর কীর্তি
(শিশুপাঠ্য গল্প)
সুভাষ চ্যাটার্জি
[প্রাককথন : কথামালার গল্পে আছে কীভাবে এক খরগোশ বুদ্ধিবলে অত্যাচারী সিংহকে কুয়োয়
ফেলে হত্যা করেছিল।তার চার পুরুষ পরে সেই খরগোশের নাতির নাতি খরু ও সেই সিংহের নাতির নাতিকে নিয়ে এই শিশুপাঠ্য গল্প। যাঁরা নিজেদের শৈশবকে ফিরে পেতে চান, তাঁদেরও ভালো লাগবে।]
(১)
হঠাৎ কয়েকজন লোক এসে খাঁচার দরজা খুলে খরগোশের বাচ্চা, মানে, আমাদের খরুকে ছেড়ে দিল। মানুষের সমাজে নাকি নতুন আইন হয়েছে, বনের জীবজন্তুদের আটকে রাখা চলবে না। খরু তো প্রথমে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা। কিছুক্ষণ খোলা দরজার বাইরে মাথা বের করে দেখল এদিক ওদিক।তারপর সোজা একদৌড়ে বনের দিকে – যেখানে তার বাবা-মা সবাই আছে।
খরগোশের মা তখন অনেকগুলো গাজর নিয়ে বসে এক মনে চিবোচ্ছিল। ঠিক সেই সময় খরগোশ দৌড়ে ঘরে ঢুকতেই খরগোশের মা তাকে দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, “ওরে আমার খরু রে! বাছা, এতদিন কোথায় ছিলি? আমরা এদিকে কেঁদে কেঁদে সারা। ভাবতাম, নচ্ছার সিংহটা বোধহয় আমার দুধের বাছাকে….।” আর কথা শেষ করতে পারে না খরগোশের মা। কান্নায় গলা বুঁজে আসে। এদিকে চেঁচামেটি শুনে খরগোশের বাড়ির সামনে বনের জন্তু-জানোয়ারদের ভিড় লেগে যায়। তারা সবাই খরগোশদের খুব ভালোবাসতো; আবার তাদের বুদ্ধির জন্য সম্মানও করত। কারণ, তারা জানতো যে খরগোশের দাদুর দাদু তাদের রাজা সিংহের দাদুর দাদুকে কিভাবে বুদ্ধির জোরে কুয়োয় ফেলে হত্যা করেছিল। কথামালার গল্পে তো সেই কাহিনী আছেই। খরুও সেই গল্প তার মায়ের কাছে শুনেছে। সে তো সেই বংশেরই ছেলে।তারও বুদ্ধি কম কিসে? বরং বেশ কিছুদিন মানুষের কাছে থেকে তার বুদ্ধিটা আরো একটু পাকা হয়েছে। তাই সবাই যখন জিজ্ঞাসা করল, খরু এতদিন কোথায় ছিল, সে কিন্তু বলল না যে সে খাঁচায় বন্দি ছিল। সে বেশ গম্ভীর ভাবে ভারিক্কিচালে বলল, “তোমরা সবাই জানো, আমার পূর্বপুরুষ খরগোশ বনের জন্তুদের কিভাবে এক সিংহের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিল, সিংহকে কুয়োর মধ্যে ফেলে। আর আমি গিয়েছিলাম মনুষ্য সমাজে বন্যপ্রাণীদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে।” সব জন্তুরা তখন সমস্বরে আগ্রহের সঙ্গে চিৎকার শুরু করে দিল, “আমরা শুনবো, সেসব কথা আমরা শুনব।” খরুর মা তখন বলে উঠল, “বাছা আমার সবে এতখানি রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছে। এখনও নাওয়া – খাওয়া হয়নি; বাছাকে এখন একটু বিশ্রাম নিতে দাও। তোমরা পরে শুনো ওর কথা।” খরু বললো, “এখানে তো সবাই আসেনি, তোমরা বরং সবাইকে খবর দাও কাল সকালে বড় বটগাছের নীচে জড়ো হতে। সেখানেই আমার সব কথা বলব।”
সব জন্তুরা তখন বলল, “সেই ভালো।” তারা তখন সবাইকে খবর দিতে যে যার মত চলে গেল।
পরদিন সকালে মিটিং শুরু হল। খরগোশ একটা উঁচু পাথরের উপর বসে; আর তার চারপাশ ঘিরে মাংসাশী, নিরামিষাশী সব প্রাণীদের ভীড়। সবাই উদগ্রীব খরুর কথা শুনতে। খরু একবার আড় চোখে সিংহের দিকে তাকালো। সিংহ রাগত চোখে তার দিকেই তাকিয়ে। মনে মনে ভাবছে, একবার সুযোগ পেলে এক থাবা মেরে জাতশত্রুটাকে শেষ করে দেবে। বিচ্ছু খরগোশগুলোর জন্য পশুরাজের সম্মান ধুলোয় লুটিয়েছে। বনের জন্তুগুলো আড়ালে হাসাহাসি করে। সিংহের দিকে তাকিয়ে খরুর বুকটা কাঁপছিল। সে সিংহের রাগ কমাবার জন্য মনে সাহস এনে বলল, ‘‘আমি পশুরাজকে এই মিটিং এর সভাপতি হতে অনুরোধ করছি।” আর সব জন্তুরা পা-তালি দিয়ে সেই প্রস্তাব সমর্থন করল।
খরু বলতে শুরু করল, “মানুষদের সার্কাসে ঢুকে দেখলাম, বাঘ সিংহরা খাঁচায় বন্দী আর চাবুক মেরে মানুষ তাদের দিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। দেখে আমার খুব দুঃখ হলো।” এই বলে সিংহের দিকে চোখ পড়তেই সে দেখলো, সিংহ তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, “গন্ডার, হাতি, বানর, পাখি, সাপ, কুমির – এদেরও সবাইকে দেখলাম চিড়িয়াখানার খাঁচায় মানুষ বন্দী করেছে।” সবাই এই কথা শুনে একসঙ্গে ধিক্কার দিয়ে উঠলো, “শেম, শেম”।
খরু আবার শুরু করল, “আমি মানুষদের ডেকে মিটিং করে বললাম, “এসব চলবে না। তোমরা যেমন দেশে দেশে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছো; আমাদের স্বাধীনতাও তোমাদের সেই রকম মানতে হবে।। বনে-জঙ্গলে থাকলেও আমরাও তো মানুষ, থুরি প্রাণী। এইভাবে আন্দোলন করে বনের প্রাণীদের রক্ষার জন্য মানুষের সমাজে পশু সংরক্ষণ আইন তৈরি করিয়ে তবে আমি ফিরছি।” সবাই খরগোশকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে উঠল, “সাধু, সাধু।” খরগোশের জয়জয়কার শুনে সিংহ রাগে ফুলতে লাগল। কিন্তু এতগুলো বনের প্রাণীর সামনে পুঁচকে একটা খরগোশের উপর রাগপ্রকাশ করলে তার রাজ-আভিজাত্য ক্ষুন্ন হবে বলে সে নীরবে রাগ হজম করল। খরু সিংহের মনোভাব বুঝতে পারল। সে ভাবলো তার ওপর রাজামশাইয়ের রাগটা যদি সে কমাতে পারে তাহলে বনে সে নির্ভয়ে শান্তিতে বাস করতে পারবে।
সবাইকে শান্ত করে খরু আবার শুরু করল, “আমাদের মধ্যে যেমন সাদা, কালো, বাদামি, হলুদ ইত্যাদি নানা রঙের প্রাণী আছে। মানুষের মধ্যেও তেমনি সাদা,কালো, বাদামী রঙের নানা জাতি আছে। এক সময় এরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করত। এখন এরা বুঝতে পেরেছে লড়াই নয়, শান্তির মধ্যে দিয়েই সকলের উন্নতি সম্ভব। বনের প্রাণীদেরও উন্নতি করতে হলে লড়াই বন্ধ করে মিলেমিশে থাকতে হবে। সাদা রঙের প্রাণী হিসাবে আমার এ ব্যাপারে আমার একটা দায়িত্ব আছে। কারণ সাদা রং শান্তির প্রতীক। চার পুরুষ ধরে পশুরাজের পরিবারের সঙ্গে আমাদের যে ঠান্ডা লড়াই চলে আসছে তার অবসান ঘটাতে আমি ঘোষণা করছি, যে কুয়োর মধ্যে পশুরাজের দাদুর দাদু পড়ে মারা গিয়েছিলেন, সেই স্থানে আমি তার স্মৃতিতে একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই।”
খরুর কথা শেষ হওয়ার আগেই পশুরা তার জয়ধ্বনি করে উঠলো। খরু আবার বলতে শুরু করলো, “আমি মানুষদের দিয়ে সেই মূর্তি বানিয়ে কুয়োর ভেতর রেখে এসেছি। পশুরাজকে অনুরোধ করছি, সেই মূর্তির গলায় মালা দিয়ে উদ্বোধন করতে।” এই প্রস্তাবে পশুরা শুয়ে পড়ে চার পা শূন্যে তুলে জোড়া পায়ে জোড়া তালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। সিংহী রাণী এতক্ষণ সিংহের পাশে বসে চুপ করে সব শুনছিল আর দেখছিল। খরগোশের কথায় ভয় পেয়ে সে পশুরাজের কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপিচুপি বলল, “শয়তানটার মতলব আমার ভালো মনে হচ্ছে না। ও তোমাকেও কুয়োয় ফেলার ফন্দি আঁটছে। তুমি ওখানে যেও না।”
সিংহ বলল, “আমি না গেলে সবাই বুঝবে, আমি ভয় পেয়েছি। সকলে হাসাহাসি করবে। সে হয় না। বরং সবাইকে নিয়েই সেখানে যাব। সকলের চোখের সামনে তেমন কিছু করতে ও সাহস পাবে না।”
এর মধ্যেই পাখিরা সব ঠোঁটে করে ফুল তুলে আনতে লাগলো। বানর মালা গাঁথার জন্য বড় লতা নিয়ে এলো। হই হই করে মালা গাঁথা হলো।
সব পশুরা মিছিল করে কুয়োর ধারে এলো। সবার আগে রাজা মশাই, হাতে তার ফুলের মালা। পিছে তার রানী। খরগোশ যাতে রাজার কাছে আসতে না পারে, তাই রাস্তা আটকে আটকে চলেছে। সিংহ সামনের পায়ের থাবায় মালাটা ধরে কুয়োর মধ্যে উঁকি মারল। কুয়োর মধ্যে নিজের ছায়া দেখে সিংহ ভাবলো, ‘‘না, খরগোশ মিথ্যা কথা বলেনি। ভেতরে সত্যিই একটা সিংহের মূর্তি দেখা যাচ্ছে- কি সুন্দর! যেন জীবন্ত।” তাড়াতাড়ি মালাটা ভেতরে ফেলেই সিংহ পেছনে সরে এলো।
এবার সিংহী রানী সামনে গিয়ে কুয়োয় উঁকি মারল। সেও নিজের ছায়াটাকে মূর্তি ভাবল। তারপর সরে এসে সিংহকে বলল, “মূর্তিটা কেমন যেন মেয়েলি ধরনের। একদম কেশর নেই।” সিংহ বলল, “না, না, আমি দেখেছি কেশর আছে; আসলে অত বড় মালায় ঢেকে গেছে বলে তুমি দেখতে পাওনি।”
সবাই মূর্তি দেখে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যে যার বাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতে খরুকে গাধা বলল, “তুমি তো মানুষদের অনেক উন্নতি দেখে এলে, আর শিল্প কাজে মানুষের অবনতিটা দেখতে পেলে না? মূর্তিটা বানিয়েছে যেন কেমন ! গায়ের রংটা যদিও ঠিকই আছে, কিন্তু মুখটা ঠিক আমার মতন।
বানর গাছের ডালে ডালে ঝুলে যাচ্ছিল। গাধার কথা শুনে সে বলল গাধাকে, “চোখের মাথা খেয়েছ তুমি? আমি গাছের উপর থেকে পষ্ট দেখলুম, মূর্তির মুখটা বানরের মতো। তারপর খরগোশকে শুনিয়ে বলল, “যতই ঝগড়া থাকুক রাজার সঙ্গে। দাদুর দাদু বলে কথা। মূর্তির মুখটা এমন পাল্টে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।”
আর সবাই বলল, “রাজা মশায়ের যখন মূর্তি পছন্দ হয়েছে, তখন আমাদের ছোট মুখে বড় কথা বলার দরকার কি?”
খরু সব শুনে কিছু না বলে আর সব প্রাণীদের বোকা বানিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি চলে গেল।
(২)
বনের যত ঘাস-পাতা খাওয়া নিরিমিষী প্রাণীদের জড়ো করে খরু বললে, “শান্তিতে বনে থাকতে হলে আমাদের রাজা বদল করতেই হবে। সিংহের বদলে কোন নিরিমিষী প্রাণী রাজা হলে আমাদের আর ভয় থাকবে না; তখন সারা বনের নীতি হবে অহিংসা।”
খরগোশের কথা শুনে সবাই তো অবাক। বলে কী? রাজা বদল ! কোনদিন হয়েছে না কেউ শুনেছে? সিংহই বা মানবে কেন?
খরগোশ বলল, “কেন হবে না? মানুষের দুনিয়ায় আখছার হচ্ছে। বনে এতদিন হয়নি বলে এখন হতে বাধা কি? একে বলে গণতন্ত্র, সবাই মিলে যাকে রাজা বানাবে সেই রাজা হবে। সিংহকেও সেটা মানতে হবে।
গন্ডার বললো, “কিন্তু রাজ্য চালাতে তো অনেক বুদ্ধি লাগে, ঘাস পাতা খেয়ে আমরা অত বুদ্ধি কোথায় পাবো?”
খরগোশ বললো, “দেখে এলাম, গরুর দুধ খেয়ে মানুষের বাচ্চারা কঠিন কঠিন অংক কষছে; গরু তো ঘাস খেয়েই এই দুধ দেয়। কাজেই ঘাস পাতায় বুদ্ধি হয় না, তা ভাবা ঠিক নয়।”
বানর গাছের উপর থেকে বলল, “বটেই তো, বটেই তো, খরগোশের যে এত বুদ্ধি – সেও তো ঘাস পাতা খেয়েই।” খরগোশ লাল চোখ দুটো উঁচু করে বানরের দিকে তাকাতেই বানর পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।।
তখন টিয়া পাখি বলল, “কিন্তু রাজা কে হবে?”
খরগোশ বললো, “আমাদের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী হাতি, সে বুদ্ধিমানও বটে। আমি তাকেই রাজা করতে প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনারা সবাই বিবেচনা করুন।”
কেউ কিছু বলার আগেই হাতি বলল, “বনে আজকাল আমার সারা বছরের খোরাক জোগাড় হয় না। তাই বছরের অর্ধেকটা সময় আমাকে বনের বাইরে খাবারের সন্ধানে যেতে হয়। সুদূর চন্দননগর, সিঙ্গুর পর্যন্ত এমনকি আমি চলে যাই দলবল নিয়ে। সুতরাং এই অবস্থায় আমার পক্ষে রাজার গুরুদায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়।”
তখন সবাই মিলে ধরল গন্ডারকে। গন্ডার বললো, “হাতি দাদার মতো আমার অত বুদ্ধি নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা খড়্গ আর সেটাই আমার কাল হয়েছে। তাছাড়া আমার হার্টের অসুখ আছে; দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে গেছে। পাগুলো এত বড় শরীরের ভার ঠিকমতো বইতে পারে না। এই শরীর নিয়ে রাজকার্য আমি চালাতে পারবো না।”
খরগোশ ভীষণ মুশকিলে পড়ল। সে হরিণকে বলল, “দেখ, বাঘ সিংহ সব থেকে বেশি তোমাদের ওপর অত্যাচার করে। যেটা বন্ধ করতে তোমারই রাজা হওয়া উচিত। তোমার চেহারাটাও রাজা হওয়ার উপযুক্ত।”
হরিণ বলল, “দায়িত্ব নেওয়ার অভ্যাস তো আমার তেমন নেই; বুদ্ধিশুদ্ধিও আমার পাকা নয়। তবে তুমি যদি মন্ত্রী হয়ে আমাকে পরামর্শ দাও, তাহলে আমার আপত্তি নেই।”
খরগোশ তো এটাই চাইছিল। সে সবিনয়ে বলল, “বনের প্রাণীরা চাইলে তাদের মঙ্গলের জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।”
তখন সবাই সমস্বরে হরিণকে রাজা আর খরগোশকে মন্ত্রী বলে ঘোষণা করল। খরগোশের কথায় হরিণ ঘোষণা করল, “আজ থেকে এই বনের নীতি হবে অহিংসা। এই বনের ভেতর কোন প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করতে পারবে না। বাঘ-সিংহরা নদী থেকে মাছ ধরে খেতে পারবে অথবা গ্রামে গিয়ে মানুষ, গরু, ছাগল ধরে খেতে পারে।”
শিয়াল গর্ত থেকে মুখ বের করে লুকিয়ে লুকিয়ে সব শুনছিল। সে চুপি চুপি দৌড়ে গিয়ে বাঘ সিংহকে সব খবর দিল। বাঘ সিংহ হুংকার ছাড়তে ছাড়তে এসে হাজির সভাস্থলে। ভয়ে হরিণের পা কাঁপতে লাগলো। খরগোশ একটু পাথরের আড়ালে সরে গেল। কিন্তু এদের দলে হাতি আর গন্ডারকে দেখে বাঘ সিংহ রাগ দমন করে বলল, “আমরা মাংসাশী প্রাণীরা তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই না। আমাদের জন্য আলাদা রাজ্যের ব্যবস্থা হোক।”
হরিণ বলল, “তোমরা একসঙ্গে থাকতে রাজি না হলে অগত্যা তাই হোক। তোমরাই বল, বনের কোন দিকটা তোমরা নেবে।”
বাঘ বলল, “পশ্চিমের গ্রামে আমাদের ছাগলটা বাছুরটা শিকারে যেতে হবে, কাজেই বনের পশ্চিম দিকটা আমরা নেব। পুবের নদীতে জল খেতে তো যেতেই হবে,তাই সেদিকেরও একটা অংশ আমাদের দিতে হবে। বনের মাঝখানটা পুরোটা তোমাদের; তাছাড়া নদীর লাগোয়া পুব বনের কিছুটা অংশও তোমরা পাবে।”
হরিণ বাঘের প্রস্তাবের ভালো-মন্দ বুঝতে না পেরে খরগোশের দিকে চাইল। খরগোশ হরিণের কানে কানে বলল, “ভালোই হয়েছে; দু’পাশে বাঘ সিংহের রাজত্ব পেরিয়ে মানুষরাও আর চট করে এখানে শিকারে আসতে পারবে না।” কাজেই বন ভাগের প্রস্তাব বিনা বাধায় পাশ হয়ে গেল।
সিংহ বলল, “বনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে জল খেতে যাবার অধিকার কিন্তু আমাদের থাকবে।”
হরিণ বলল, “আমরা তো তোমাদের আলাদা করে দিইনি, তোমরা নিজেরাই আলাদা হচ্ছো। আমাদের রাজ্য দিয়ে যাতায়াতে তোমাদের কোন বাধাই নেই। তবে আমাদের রাজ্যের ভেতর তোমরা কোন পশু মারতে পারবে না।”
বাঘ বলল, “আমাদের অংশে কিন্তু তোমরা কেউ ভুল করে ঢুকে পড়লে ছাড়া পাবে না। তখন আমাদের দোষ দিও না।”
বন তো ভাগ হয়ে গেল। শিয়াল চলে গেল বাঘ সিংহের সঙ্গে; ওদের খাবার থেকে কিছুটা তো সে ভাগ পাবে।
কুকুর বিড়াল তখনো বনেই থাকত। ওদের হল মহা মুস্কিল। বিড়াল বললো, “আমি ইঁদুর টিঁদুর ধরে খাই। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। খাব কি? কুকুর বলল, “বাঘ সিংহের সাথে গেলে মাংসের ছিটেফোঁটা ভাগ জুটে যেতেও পারে; কিন্তু তার থেকেও নিজেই মাংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।” তখন দুজনে যুক্তি করে বলল, “চলো, এবার বনের পাট উঠিয়ে দিয়ে মানুষের সঙ্গে গ্রামে গিয়ে থাকি। মানুষরা অনেক রকম খাবার বানাতে পারে, মুখ বদলে সেগুলোর স্বাদ নেওয়া যাবে। তখন কুকুর আর বেড়াল বন থেকে মানুষের গ্রামে চলে এলো। সেই যে মানুষের কাছে এলো আর কোন দিন বনে ফিরে গেল না। সেই থেকে কুকুর বেড়াল মানুষের সমাজের প্রাণী হয়ে গেল।
এদিকে বাঘ সিংহরা আলাদা রাজ্যে গেছে বলে তো আর উপোস করে নেই। শেয়াল গিয়ে খবর দেয়, তাদের সীমানার কাছে হরিণের বাচ্চারা খেলা করছে অথবা কেউ জল খেতে গিয়ে দলছুট হয়ে একলা ঘুরছে। বাঘ সিংহ এক লাফে গিয়ে তাদের ধরে নিয়ে চলে আসতো। তারপর আয়েস করে খেত। এসব খবর হরিণের কানে আসতে লাগল। হরিণ খরগোশকে বলল, “মন্ত্রী, এর তো একটা বিহিত করতে হয়।”
খরগোশ বললো, “রাজা মশাই, কিচ্ছু ভাববেন না। আমি এক্ষুনি একটা তীব্র প্রতিবাদ পত্র লিখে পাঠাচ্ছি; বাছাধনরা মজা টের পাবে।”
বাঘ সিংহরা খাওয়া-দাওয়া সেরে গাছের ছায়ায় আরাম করছিল। শিয়াল অদূরে তাদের এঁটো খেয়ে পরিষ্কার করছিল। এমন সময় গাছের উপর থেকে বানর হুপ করে একটা ডাক ছাড়লো। শিয়াল বললো, “কে রে?” বানর বলল, ‘‘আমি হরিণ রাজার দূত। আমি তীব্র-প্রতিবাদ-পত্র দিতে এসেছি।” এই বলে গাছের ওপর থেকে সিংহের মুখের সামনে চিঠিটা টুক করে ফেলে দিল।
চিঠির ছোঁয়ায় সিংহের গোঁফে সুড়সুড়ি লাগতেই তার ভাতঘুম থুড়ি, মাংস-ঘুম ভেঙে গেল। সে রেগে মেগে চিঠি খুলে পড়েই আরো রেগে গেল। বানর গাছের উপরে থাকায় তাকে কিছু করতে পারল না। তাকে বলল, “তোদের রাজাকে বলবি, আমাদের রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যারা সীমানা পেরিয়ে ঢুকেছিল, তারাই কেবল মরেছে।”
হরিণ খরগোশকে বলল, “এখন উপায়?” খরগোশ বললো, “এই সমস্যার সমাধানে মানুষরা সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া বসায়। কিন্তু আমরা তো রাজ্যে ওদের ঢোকার অধিকার মেনে নিয়েছি। এখন বেড়া দিলে এরা আমাদের চুক্তিভঙ্গের জন্য দায়ী করবে। পশু-অধিকার কমিশনে গিয়ে নালিশও করতে পারে।”
এদিকে বন ভাগ হওয়ায় খাবারের জন্য ঘাস পাতারও অভাব দেখা দিল নিরিমিষী প্রাণীদের। তাদের অংশের গাছপালাগুলো ন্যাড়া হয়ে যেতে লাগল। আবার বাঘ সিংহের অংশের গাছপালা, ঘাস সব সবুজে ভরে গেল। সেই খাবারের লোভে সীমানার ধারে এলেই বুনোমোষ, হরিণরা বাঘ সিংহের শিকার হতে লাগলো।হরিণ তখন খরগোশকে বলল, ‘‘শিগগির একটা উপায় বের করো।”
খরগোশ বলল, “রেশনিং”।
হরিণ বলল, “সেটা আবার কি গাছ?”
“আহা,গাছ নয়, গাছ নয়। সবার খাবারের পরিমাণ বেঁধে দিতে হবে। যত খুশি খাবে, তা চলবে না। মানুষের সমাজে এটা আছে, সেখানে এমনকি জল, আলো, হাওয়া সবকিছুই রেশনিং হয়।”
খরগোশের কথায় সব জন্তুরাই গেল ক্ষেপে। হাতি বলল, ‘‘এমনিতেই তো সারা বছর বন থেকে পুরো খাবার পাই না; তারপরে যেটুকু জোটে তার ওপরে আবার ছাঁটাই !”
গন্ডার বললো, “বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারি না, খাবারের জন্য এক জায়গায় যা পাই, তাই খাই। সেটাও এরা দেবে না !”
বনের প্রাণীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে দেখে হরিণ খরগোশকে বলল, “ওসব করলে ফল ভালো হবে না, অন্য কিছু কর।”
খরগোশ ভাবল, এখন ক’দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকাই মঙ্গল। মুখে বলল, “আমি বরং মানুষের গাঁয়ে গিয়ে জেনে আসি, এখন কি করা উচিত। এই বলে সে তখনই বেরিয়ে পড়ল গ্রামের দিকে। বনের সীমানার কাছে আসতেই পড়বি তো পড়, একেবারে শিয়ালের সামনে। শিয়াল তাকে নড়বার সুযোগ না দিয়ে মুখে তুলে নিয়ে সোজা এক দৌড়ে সিংহের সামনে হাজির হলো। মুখ থেকে তাকে নামাবার আগেই খরগোশ সিংহের উদ্দেশ্যে বলল, ‘‘পেন্নাম হই রাজা মশাই।আপনার কাছেই আসছিলাম।এতখানি রাস্তা আসতে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল; তাই শিয়ালকে বলতে ও আমাকে মুখে করে বয়ে নিয়ে এলো।”
সিংহ সন্দেহের দৃষ্টিতে খরগোশের দিকে তাকিয়ে বলল, “তা মতলবটা কি বলে ফেলো দেখি।” খরগোশ বললো, “দেখুন গায়ে রাজরক্ত না থাকলে কি রাজকার্য চালানো যায়? তাই আপনাকে রাজপদে বরণ করতে নিয়ে যেতে এলাম। এখন আপনি রাজি হলেই হল।” সিংহ খুশি হয়ে দলবল নিয়ে খরগোশের সঙ্গে তখনই রওনা হল।
এদিকে নিরিমিষী প্রাণীরা খরগোশের সঙ্গে বাঘ সিংহকে দেখে অবাক হয়ে গেল। তখন খরগোশ তাদের আলাদা ডেকে বলল, “বাঘ সিংহের রাজ্যের গাছপালাগুলো কেমন সবুজ পাতা, ডালপালায় ভর্তি দেখেছো? যাতে খাদ্যের অভাব না হয়, সেইজন্য কৌশলে বাঘ সিংহকে এখানে ডেকে ওদের রাজ্য খালি করেছি। যে যত পারো সেখানে গিয়ে গাছ পাতা খাও। নো রেশনিং !” সবাই তাই শুনে খুশি হয়ে বলল, ‘‘থ্রি চিয়ার্স ফর খরগোশ! হিপ হিপ হুররে!”
—ooo—
S10
কদমা
সুভাষ চ্যাটার্জি
ছোটবেলায় দেখতাম, বাড়িতে সরস্বতী ও লক্ষ্মীপূজোয় চিনির কদমা আর লাল, সাদা ও হলুদ রঙের মঠ আসত। মঠের আবার কত রকম গড়ন– মাছ, পাখি, হাতি, ঘোড়ার আদলে। ওগুলো খেতে আমি খুব ভালোবাসতাম। আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, কখন পূজো শেষ হবে আর ওগুলো প্রসাদ হয়ে আমার হাতে আসবে। তারপর হাত থেকে মুখে উঠতে তো কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার।
কিন্তু পূজো শেষের পর মা আমাদের ভাইবোনদের গোটা একটা মঠ কখনো দিত না, একটা ভাঙা অংশ খালি পেতাম। আর কদমাগুলো এতই শক্ত ছিল, যে মা সেগুলো ভাঙতে পারত না; তাই কদমা একটা গোটা পেতাম, কিন্তু তার বেশী হোত না। মা বলতো, এগুলো বেশি খেলে নাকি দাঁতে ও পেটে পোকা হয়। ছোটবেলায় আশ মিটিয়ে কদমা, মঠ খেতে না পাওয়ার একটা আক্ষেপ আমার মনে বরাবর ছিল। তাই, স্কুলে পড়ার বয়সেই আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম, চাকরি পেলে প্রথম মাইনের টাকায় মনের সুখে কদমা আর মঠ খাব।
এর একটা ভালো দিক ছিল। মঠ খেতে হলে চাকরি পেতে হবে আর চাকরি পেতে হলে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে,আর ভালো ফল করতে হলে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে– এই ভাবনাটা আমার মনে একটা অনুপ্রেরণার কাজ করত। তাই, পড়াশোনা শেষ করে পরীক্ষা দিয়ে চাকরির চেষ্টা শুরু করে দিলাম। তবে চাকরি পাওয়াটা সেকালেও খুব সহজসাধ্য ছিল না।
যাই হোক, অনেক চেষ্টার পর শেষমেষ কোলকাতায় একটা চাকরি জুটে গেল। দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। কী আনন্দ! মাস মাইনের দিন এসে গেল, মনে কি ফূর্তি ! পে ডে, পে ডে; গে ডে, গে ডে। আজ প্রাণভরে মঠ আর কদমা খাব, একাই খাব, কাউকে ভাগ দেব না। কয়েকজন সহকর্মী আবদার জুড়ে দিল, ‘‘ভায়া, প্রথম মাইনে পাচ্ছো, খাওয়াও। পাশের দোকানে ফিস ফ্রাই থেকে সিঙাড়া সব পাওয়া যায়, দারুণ ভাজে। হবে নাকি?” আমার কাছে সেই মুহূর্তে মঠ আর কদমার তুলনায় ফিস ফ্রাই, শিঙাড়া অতীব তুচ্ছ। বললাম, “দাদা, আজ থাক, একটু তাড়া আছে। তাছাড়া, বাসে যা পকেটমারের উৎপাত; এতগুলো মাইনের টাকা সঙ্গে আছে তো। তাই, অফিসফেরতা ভীড়টা শুরুর আগেই বেরিয়ে যেতে চাই।” সহকর্মী ব্যাজার মুখে বলল,‘‘ঠিক আছে, সাবধানে যাও।”
বাড়িতে ঢোকার আগে পাড়ার দোকানে মঠ আর কদমার খোঁজ করলাম। দোকানী বললো,‘‘এই অসময়ে এসব তো রাখি না। পূজো-আর্চ্চার সময় নিয়ে আসি। আপনার খুব দরকার হলে শিয়ালদা বৈঠকখানা বাজারে পেয়ে যাবেন।” শুনে মনটা একটু মুষড়ে পড়ল। ভেবেছিলাম, প্রথম মাইনে পাওয়ার দিনটা ছোটবেলার একটা ইচ্ছা পূরণ করে সেলিব্রেট করব। তা আর হোল না।
পরদিন অফিস ছুটির পর সোজা শিয়ালদা বৈঠকখানা বাজারে হাজির হলাম। দেখে অবাক হলাম, এখানে এতরকম জিনিস পাওয়া যায় ! এরমধ্যে কদমা খোঁজা তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা। কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না।
এক দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলল,‘‘ দেখছেন, এটা ধূপকাঠির দোকান।” আমি ‘স্যরি’ বলে সরে পড়লাম। এই ভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে এ গলি সে গলি ঘুরে অবশেষে সেই সাত রাজার ধন মানিকের সন্ধান পেলাম।
দোকানী খবরের কাগজের ঠোঙায় ভর্তি করে মঠ আর কদমা দিল। আমার ইচ্ছা করছে, এখানে দাঁড়িয়েই কদমা আর মঠগুলো টপাটপ মুখে পুরে দিই। কিন্তু এত লোকের মাঝখানে বাচ্চাদের মতো মঠ খেতে বাধো বাধো ঠেকলো।
একটু হেঁটে গিয়ে ফাঁকা মতো একটা পার্কে বেঞ্চে বসে ঠোঙা খুলে একটা মঠ গোটাটাই মুখে দিলাম। এত মিষ্টি যে গা-টা গুলিয়ে উঠল। এরপর একটা কদমায় কামড় দিলাম। বাপ রে! কী শক্ত। দাঁতে কাটতে পারলাম না। পাশে রাখা ডাস্টবিনে মঠ ও কদমাসুদ্ধ ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।
মনের মধ্যে আবাল্য লালিত সুপ্ত ইচ্ছাটা ডাস্টবিনের গহ্বরের অন্ধকারে এক লহমায় মিলিয়ে গেল।
—০০০—
S11
জীবনমুচির জীবন
সুভাষ চ্যাটার্জি
সরু খালের মতো একটা শীর্ণ নদী। বছরের অধিকাংশ সময় জল থাকে না। কিন্তু, ডিভিসি বাঁধের থেকে জল ছাড়লে ফুলে ফেঁপে উঠে দু’কূল ছাপিয়ে বান আসে। তার একটা বাঁকের ধারে জীবনমুচির কুঁড়েঘর। ওখানে নদীর পাড়ে পরপর চার ঘর মুচির বাস। তার সামনে দিয়ে কাঁচা মাটির রাস্তা। রাস্তার অন্য পাশে ভগ্নপ্রায় জোড়া শিবমন্দির। আশেপাশে ইঁটের তৈরী আরও কিছু ভগ্নাবশেষ। এককালে মন্দির চত্বর যে বেশ বড় ছিল,তা বোঝা যায়। পাশে বিশাল বটগাছ তার ঝুরি বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা বরাবর দু’দিকে আরো কিছু ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে সাপ বেরিয়ে রাস্তা এপার ওপার করে। ঐ রাস্তায় মাইলখানেক হেঁটে আমি স্কুলে যাই। রাস্তাটা এমনিতে নির্জন। আমার ভীষণ ভয় করে।ভয়ের আরও কারণ আছে; মুচিপাড়া থেকে সামান্য আগেই একটা মৃত পশুর ভাগাড়। ওখানে মরা পশু ফেলে গেলে মুচিরা চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে মুচিপাড়ার গায়ে একটা পরিষ্কার সমতল জায়গায় কাঠের খোঁটা পুঁতে, চামড়াতে তেল জাতীয় কিছু মাখিয়ে টানটান করে শুকোতে দেয়; তাকে ওরা বলে ট্যানিং। আর পাশের একটা বড় গাছের উপর শকুনের দল বিচিত্র আওয়াজ করে অপেক্ষা করতে থাকে ছাল ছাড়ানো পশুর মাংস খাবে বলে।
যেদিন ভাগাড়ে কোন পশুর দেহ থাকে না, সেদিন শকুনের দল জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমাকে ওদের খাদ্য মনে করে কিনা কে জানে।আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। আমি ভয় পেলে ‘জীবনদা, জীবনদা’ বলে জোরে জোরে ডাকি।জীবনদা আমাকে চেনে। ও বাজারে জুতো সারাতে বসে। আমি ছুটির দিনে বাবার জুতো সারাতে আর পালিশ করাতে ওর কাছে যাই; আর ওর সাথে গল্প করি। শনিবারের নিঝুম দুপুরে স্কুলের হাফ ছুটির পর ওর বাড়ির সামনের রাস্তায় ফিরতে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।জীবনদা ঐ সময় দুপুরের খাবার খেয়ে গরমকালে আম গাছের নিচে বসে; আর শীতকালে রোদে বসে হুঁকো খায়। আমি জীবনদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঐ জায়গাটা পার হয়ে আসি। জীবনদা আমাকে সাহস দেওয়ার জন্য বলে, শকুনরা কোন জ্যান্ত প্রাণীকেই কিছু করে না। ওরা শুধু মৃত প্রাণীর দেহই খায়।
জীবনদার একটা পোষা কুকুর আছে; ওর নাম ভুলু। ও জীবনদার খুব বাধ্য। জীবনদা ওকে বলে আমার সঙ্গে গিয়ে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসতে। ও জীবনদার কথা বোঝে; আমার সঙ্গে আসে ভাগাড়ের শেষ সীমা পর্যন্ত। তারপর দাঁড়িয়ে থাকে আমাকে যতক্ষণ দেখা যায়। আমি পেছন ফিরে হাত নাড়ি, ও তখন চলে যায়। ভুলুর সাথে আমারও খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমি মুচিপাড়া বা ভাগাড়ের কাছে এসে জোরে ‘ভুলু’ বলে ওকে ডাকলে ও একছুটে লেজ নাড়তে নাড়তে আমার কাছে চলে আসে।তারপর আমাকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে যায়।
আমি জীবনদার কাছে জুতো সারাতে গিয়ে গল্প করতে করতে জেনেছি, জীবনদা রোজ সকালে আটটা নাগাদ বাজারে আসে। তারপর বাজারের একপাশে তার বসার জায়গায় একটা লাঠির মাথায় জীর্ণ ছাতাখানা সযত্নে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখে।তার নীচে জীবনদা বসে তার জুতো সারাবার সরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি থেকে আনা রুটি গুড় দিয়ে সকালের আহার সারে। দুপুর একটার পর উপার্জনের পয়সা দিয়ে সামান্য তেল, নুন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বাড়ি ফেরে।জুতোর সরঞ্জাম ও মুদিখানার জিনিস নামিয়ে, ছাতাটা ঘরের এককোনে দাঁড় করিয়ে সে জঙ্গল থেকে শাকপাতা, কচু, মেটে আলু বা বাড়ির চালের কুমড়ো, লাউ এসব জোগাড় করে। মাঝেমধ্যে নদীতে বা পুকুরে ছিপ ফেলে মাছও ধরে।মাছ পেলে অতি সামান্য তেলে আধভাজা আধপোড়া মাছ দিয়ে ওদের মহাভোজ হয়। আমি সেদিন ওদের বাড়ির সামনে যাওয়ার সময় মাছ ভাজার গন্ধ পাই। এই ভাবে ওদের রোজকার খাবার জোগাড় হয়।খাবারের ব্যবস্থা করে জীবনদা কাঁচা চামড়ার সন্ধানে যায়।তারপর ট্যানিং এর ব্যবস্থা করে পুকুরে স্নান সেরে খাওয়া দাওয়া করে।
জীবনদার গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। স্কুল থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে গাছ তলায় বসে আমি গল্প শুনি।জীবনদা আমাকে বলেছে, শকুনদের দলের লাল মাথাওয়ালা রাজা আছে। সে যতক্ষণ না খাবে, ততক্ষণ অন্য শকুনেরা পশুর দেহ খায় না। রাজা প্রথম খায়, তারপর অন্যরা খায়। শুনে আমার খুব মজা লাগে।
গরমের ছুটিতে স্কুল যাওয়া বন্ধ।জীবনদার সঙ্গেও দেখা হয় না। তাই বাবা জুতো পালিশ করাতে যেতে বলাতে আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্যাগে জুতো ভরে বাজারের দিকে চললাম। জীবনদা যেখানে বসে, সেখানে দেখি জীবনদা নেই। আশপাশের বাজারের লোকদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, জীবনদার শরীর খারাপ, তাই বেশ কয়েকদিন ধরে আসছে না। আমি তখনই জীবনদার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।
জীবনদার বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখলাম, ভাগাড়ের পাশে নদীর ধারে মুচিপাড়ার লোকেরা জড়ো হয়েছে।জীবনদা হয়তো এখানেই থাকবে, এই ভেবে আমিও ওখানে গেলাম।
হ্যাঁ, জীবনদা এখানেই আছে। কিন্তু জীবনদা আর নেই।জীবনদার নিষ্প্রাণ শরীরটাকে নদীর পাড়ে একটা খাটিয়ার উপর শোয়ানো হয়েছে। পাশেই চিতা সাজাবার কাজ চলছে।ভুলু আমাকে দেখে নীরবে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আজ আর ও লেজ নাড়ছে না। ও বুঝতে পেরেছে, ওর একজন কাছের লোক চিরকালের জন্য চলে গেল। আমি ওকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। ও আমার হাত চেটে সমবেদনা জানাল।
যে শকুনের দল নীচে প্রাণীর দেহ দেখে খাওয়ার আনন্দে কোলাহল শুরু করে দেয়, তারাও আজ নিস্তব্ধ, সামান্য নড়াচড়াও করছে না। বোধহয় ওরাও বুঝতে পেরেছে, এতদিন যে লোকটা ওদের খাবার সাজিয়ে দিয়েছে পশুর দেহকে চামড়ামুক্ত করে, সে আর কোনোদিন আসবে না তাদের খাবার নিয়ে।
—০০০—
S12
শুক্লপক্ষ
সুভাষ চ্যাটার্জি
আমার একটা নেশা আছে।গল্পের বই পড়ার।বড় গল্প নয়,ছোট ছোট বাংলা গল্প।কখনও কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের, আবার কখনো উঠতি কোন লেখকের। উপন্যাস আমি পড়ি না, কারণ সেখানে পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে পুরোপুরি পরিচয় ঘটে; আমার পছন্দ ছোট গল্প যার মধ্যে চরিত্রগুলোর সঙ্গে পাঠকের স্বল্প পরিচয়ের পরই গল্পের সমাপ্তি ঘটে। তারপরই শুরু হয় আমার খেলা– আমি আমার মতো করে গল্পের নায়িকার সঙ্গে পরিচয় করে নিই, তার সঙ্গে কথা বলি, গল্প করি, মানস-ভ্রমণে যাই। এইভাবে দিনের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো খুব মজা করে কাটাই। আবার যখন নতুন গল্প পড়ি, তখন পুরনো নায়িকার বদলে নতুন নায়িকার সঙ্গে নতুন বন্ধুত্ব শুরু হয়।
দু‘দিন আগে ঠিক এরকমই এক গল্প পড়েছিলাম, যার নায়িকার নাম জোছনা। আসল নাম অন্য, কিন্তু নায়ক তাকে এই নামেই ডাকে। আমারও নামটা খুব পছন্দ হোল, কারণ নায়িকার বর্ণনার সঙ্গে নামটা খুব মিলেছিল। এই দুদিন ধরে জোছনার সঙ্গে আমার বেশ ভালো মানস বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।কিন্ত সেটা আমি কাউকে বলতেও যাই নি। বেগম আখতারের গান ‘জোছনা করেছে আড়ি, গলি দিয়ে চলে যায়, আসে না আমার বাড়ি’ মোবাইলে বাজিয়ে মাঝে মাঝেই শুনি আর জোছনার উদ্দেশ্যে বলি, ‘গলিতে ঢুকবে আর আমার বাড়ি আসবে না– এ তো হতে পারে না।’
হঠাৎ আজকে পাড়ার বন্ধু তপন এসে বলল,‘‘ গুরু, একটা দারুণ খবর আছে। তোদের বাড়ির পাশের গলিতে নতুন ভাড়াটে এসেছে।একটা সুইট সিক্সটিন মেয়েও আছে; নাম জোছনা।” নামটা শুনেই আমার বুকের ভেতর কেমন ধক্ করে উঠলো। আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, ‘‘ধুর, তাও আবার হয় নাকি?” তপন বলল,‘‘কি যা-তা বলছিস? কি হয় না? কেন হয় না?” আমি আমতা আমতা করে ঢোঁক গিলে বললাম,‘‘না, মানে বলছি জোছনা আবার নাম হয় নাকি? তুই হয়তো ভুল শুনেছিস।” তপন জোর গলায় বলল,‘‘ ভুল শুনেছি বললেই হলো। কাকু ,মানে ওর বাবা ওকে ঐ নামেই ডাকল, আমি স্পষ্ট শুনলাম।” আমার মনে মনে খুব রাগ হল, বললাম, ‘‘বাহ্, এর মধ্যে কাকুও বানিয়ে ফেললি? আমি বলতে চেয়েছি, নামটা হয়তো জ্যোৎস্না।” তপন বলল,‘‘হবে হয় তো। আমি অত ভালো করে শুনিনি।” আসলে আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমার জোছনাকে তপন কেড়ে নিচ্ছে।তপন সরলভাবে বলল,‘‘তোদের ছাদে চল,বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।”
তপন আমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিলেও আমার রাগ কমল না। আমার খালি মনে হচ্ছে, আমার বাড়ির একদম পাশে, অথচ আমি জানলাম না আর তপন এক ফার্লং দূরে থেকেও আগে জেনে গেল।ঐ কাঁচা বয়সে আমার ও বন্ধুদের একটা প্রিয় খেলা ছিল, পাড়ায় কোন নতুন ভাড়াটে এলে সে বাসায় কোন কিশোরী বা যুবতী আছে কিনা খবর রাখা। এই খেলায় তপন আমাকে হারিয়ে দেবে তা মেনে নিতে পারছি না।আমাকে জিততেই হবে; আমার জোছনা আমারই থাকবে।
গলিটার একদিক বন্ধ, ওখান থেকে বেরোতে গেলে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বেরোতে হবে।তাই আমি আমার বাড়ির দুয়ারে জোছনাকে দেখার আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে শুরু করলাম।দিন দুয়েকের মধ্যেই ফল পেলাম।এ পাড়ার সবাই মুখ চেনা। কাজেই একটা অপরিচিত মুখ গলির সামনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক কিছু খুঁজছে দেখে তপনের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হলাম এ-ই জোছনা।তবে তপনের কথামতো সুইট সিক্সটিন না হলেও অষ্টাদশী হবে।তাতে জোছনার আলো তো কিছু কম হবে না। নিষ্পাপ মুখ করে জিজ্ঞাসা করলাম,‘‘আপনি কি কিছু খুঁজছেন?” ও বলল,‘‘ হ্যাঁ, মানে আমরা তো এ পাড়ায় নতুন।রেশন দোকানটা কোনদিকে যদি বলেন।” আমি বললাম,‘‘ আমি তো বাজারেই যাচ্ছি, ঐদিকেই রেশন দোকান।চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।” ‘‘কিন্তু আপনার সাথে তো ব্যাগ নেই।” সর্বনাশ, এ তো উকিলের মতো জেরা করছে। শেষকালে বিপদে পড়ে যাব না তো? কথা ঘুরানোর জন্য বললাম,‘‘আজকাল তো দোকানে ক্যারিব্যাগ দেয়, তাই। আমরা যখন এক পাড়ায় থাকি, তখন আপনি আপনি না করে তুমি বলতে পারি; তাই না?” জোছনা আপত্তি না করে স্মার্টলি বলল,‘‘বলতেই পারি। কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার পরিবেশের পক্ষে ভালো না, সেটা নিশ্চয়ই জানা আছে।” উঃ, এ তো দেখছি, ভবি ভুলবার নয়। আমি ন্যাকামি করে ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম, যেন আমি কিছুই জানি না।ও নাম বলল, কিন্তু পরিবর্তে আমার নাম জিজ্ঞেস করল না। আমি গায়ে পড়ে বললাম, ‘‘আমার নাম অরুণ চন্দ্র সেন”, যদিও আমি কুমার বা চন্দ্র কিছুই ব্যবহার করি না। ও বলল, ‘‘চন্দ্র কেন? অরুণের সাথে চন্দ্র হয় না।” আমি ওভারস্মার্ট হয়ে বললাম,‘‘কেন হবে না? জ্যোছনা থাকলে চন্দ্রও থাকবে। চন্দ্র ছাড়া জোছনা হয় নাকি?” ও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। বোধহয় একটু লজ্জা পেয়েছে, নয়তো যুতসই জবাব খুঁজে পাচ্ছে না।
কথায় কথায় বাজার, রেশন দোকান এসে গেল।রেশন দোকানী মণ্টুদা আমাকে ভালোই চেনে। ওকে বললাম,‘‘মণ্টুদা, ওরা আমাদের পাড়ায় নতুন এসেছে। রেশন কার্ডটা করে দিতে হবে।” মণ্টুদা জোছনার কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়ে বলল, ‘‘ সামনের সপ্তাহে কার্ড ও রেশন দুটোই পাবে; এসে নিয়ে যেও।” এত তাড়াতাড়ি কাজ মিটে যেতে জোছনা আমাকে বলল, ‘‘তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তোমার জন্য তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল।” আমি বললাম,‘‘ধন্যবাদের কি আছে? প্রতিবেশীর দরকারে তো প্রতিবেশীরাই পাশে দাঁড়ায়। আবার কোন দরকার হলে বোলো।” ও বলল, ‘‘ নিশ্চয়ই বলব, আজ তাহলে আসি।” আমি মনে মনে বললাম, ‘‘ কী সাংঘাতিক! এত তাড়াতাড়ি ‘আসি’ বললে হবে?” আমার মনের মধ্যে বেগম আখতার যেন সাবধান করতে গেয়ে উঠল, ‘জোছনা করেছে আড়ি।’ না, না, ওর আড়ি করার পথ বন্ধ করতে হবে। আরও বেশি করে ভাব করতে হবে।
আমি বললাম,‘‘চলো, তোমাকে পোস্টাপিসটা চিনিয়ে দিই; চিঠিপত্র দিতে কাজে লাগবে।” এখান থেকে পোস্টাপিস অনেক দূর। আমার উদ্দেশ্য বেশ খানিকটা সময় কাটানো যাবে ওর সঙ্গে। কিন্তু ও বলল, ‘‘না, না, পোস্টাপিসে আমাদের দরকার নেই। চিঠিপত্রের কাজ তো ইমেইল, হোয়াটসঅ্যাপেই হয়ে যায়।” দরকার নেই বললেই হলো, আমার তো দরকার আছে। আমি বললাম, ‘‘পোস্টাপিসে আজকাল ব্যাঙ্কের কাজও হয়।” কিন্তু কাজ হলো না। ও বলল,‘‘আমাদের অ্যাকাউন্ট সব ব্যাঙ্কের সাথে। পোস্টাপিসে নেই।” আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম; বললাম, ‘‘ব্যাঙ্ক তো এই পথে সামনেই পড়বে।চলো, দেখিয়ে দিই।”
কথা বলতে বলতে আমরা ব্যাঙ্কের দিকে এগোচ্ছি। ব্যাঙ্ক এসে গেল। ও বলল,‘‘আর পোস্টাপিসে যাওয়ার দরকার নেই, এবার বাড়ি ফিরব।” দরকার নেই বললেই ছেড়ে দেব ? আমি সে বান্দা নই। ডুবন্ত মানুষের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইলাম; বলে উঠলাম, ‘‘আধার, আধার, এই পোস্টাপিসে আধারের কাজও হয়। তোমাদের তো আধারের ঠিকানা বদল করাতে হবে।” এইবার বরফ গলল। জোছনা বলে উঠল,‘‘ঠিক বলেছো, এটা তো খুব দরকার।” আমরা পোস্টাপিসের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।রোদটা বেশ চড়া। একটা ভুল হয়ে গেছে। বেরোবার সময় যদি একটা ছাতা সঙ্গে রাখতাম, তাহলে এক ছাতার তলায় দুজনে একসাথে যেতে পারতাম।
পোস্টাপিসের গায়ে একটা পার্ক আছে। আমার প্ল্যান, ঐ পার্কে বসে যদি কিছুক্ষণ গল্প করা যায়। ওখানে একটা ফুচকাওয়ালা থাকে।মেয়েদের কাছে ফুচকার মতো লোভনীয় জিনিষ আর কি আছে, আমার জানা নেই। এরকম একটা মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেলে জোছনা রূপোলী শাড়ি না হলেও লুটিয়ে পড়তে পারে।
এ যে দেখছি, মেঘ না চাইতেই জল। ফুচকাওয়ালা মাথায় ফুচকার বাক্স নিয়ে এদিকেই আসছে। হাতের নাগালে জোছনা বধের ব্রহ্মাস্ত্র ! ফুচকাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে বললাম,‘‘তুমি পার্কে যাও না?” ও বলল, ‘‘এতক্ষণ পার্কেই তো ছিলাম।এত বেলায় তো পার্কে লোক আসে না, তাই বাজারের দিকে যাই।” আমি বললাম, ‘‘আমাদের একটু ভালো করে মেখে ফুচকা খাওয়াও তো।” জোছনা বলল,‘‘তুমি খাও, আমি খাব না। আমার কাছে এখন টাকা নেই।” আমি বললাম,‘‘আমি খাওয়াচ্ছি।আর তাতেও যদি আপত্তি থাকে, পরে আমার বাড়ি এসে শোধ দিয়ে দিও।” ও বলল,‘‘ঠিক আছে; তখন কিন্তু নিতে হবে।” আহা, এই সুযোগটাই তো খুঁজছিলাম। জোছনা ফুচকাওয়ালাকে বলল, ‘‘বেশি করে ঝাল দিয়ে মাখবে।আর দুজনকে সমান সমান দেবে। তাতে ভাগের হিসেব করতে সুবিধা হবে।” আমি বললাম, ‘‘না, আমি একটা বেশি খাব। ফুচকা খাওয়াতে আমি সবসময় জিতি।” জোছনা বলল,‘‘আমার বন্ধুরাও আমাকে হারাতে পারে না।” আমি তো বিষম সমস্যায় পড়ে গেলাম।একটা বেশি খেয়ে ওকে হারানোটা কি ঠিক হবে? মান্না দের গানের কলি মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠলো,‘‘মেনেছি গো, হার মেনেছি। তব পরাজয়, মোর পরাজয়, বারে বারে তা জেনেছি।” ঠিক,ফুচকা খাওয়াতে হারিয়ে দিয়ে জোছনাকে হারাবার রিস্ক আমি নেব না। জিততে হলে আমাকে আজকে হারতে হবে। আমি বললাম, “ঠিক আছে, তবে সমান সমানই হোক।”
চড়া রোদে বেশি করে ঝাল দেওয়া ফুচকা খেয়ে পোস্টাপিসে যাওয়ার আগ্রহটা দুজনেই হারিয়ে ফেললাম।তাই এরপর দুজনেই বাড়ি ফিরে এলাম।
বাড়ি ফিরে আমার মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল। এবারে ফুচকা খাওয়ার টাকা ফেরত দিতে জোছনা নিজেই আমার বাড়ি আসবে।আমি বেগম আখতারের গানের কথা পাল্টে নতুন করে গাইব, ‘‘জোছনা করেনি আড়ি, গলি দিয়ে আসে যায়, এসেছে আমার বাড়ি।”
হ্যাঁ, পরের দিন সকালেই জোছনা ফুচকার টাকা দিতে আমার বাড়ি এসেছিল। আমার মা তো ‘‘ও মা, কী মিষ্টি মেয়ে,কী মিষ্টি মেয়ে” বলতে বলতে ওর জন্য জল আর মিষ্টি নিয়ে এল। জোছনাও ‘আমি মিষ্টি খাই না’ বলেও দুটো মিষ্টিই খেয়ে নিল।তারপর এক নিঃশ্বাসে বলল, ‘ওমা কি ভালো মিষ্টি, মুম্বাইতে এরকম পাওয়াই যায় না।কোন্ দোকানের মিষ্টি আমাকে একটু চিনিয়ে দিও, আমি বাড়ির জন্য নেব।’
এর পর মিষ্টির দোকান, রেশন দোকান, পোস্টাপিস, ব্যাঙ্ক, ইলেকট্রিক অফিস, ডাক্তারের চেম্বার আরও নানা দরকারি, অদরকারী জায়গায় জোছনার সাথে ঘুরে ঘুরে দুটো সপ্তাহ কেটে গেল।এর মধ্যে বেশ কয়েকবার জোছনা আমাদের বাড়িতে এসেছে। আজও এসেছিল।এসেই বলল,‘‘কাল আমি মুম্বাই ফিরে যাচ্ছি।মা-বাবাকে একটু গুছিয়ে দিয়ে গেলাম। বছরের মাঝামাঝি বাবার বদলি হোল। এই সময় আমার কলেজ বদল করলে সমস্যা হবে বলে বাবা আমার জন্য ওখানে হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছে। আমি হোস্টেলে থেকেই পড়ব।”
পরদিন আমি ছাদে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, জোছনা মুম্বাইয়ের ট্রেন ধরার জন্য ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, দু সপ্তাহর পর শুক্লপক্ষ থাকে না, জোছনা থাকে না; তারপর আবার কৃষ্ণপক্ষ আর অমাবস্যার অন্ধকার। আমার আকাশও এখন জোছনাবিহীন অন্ধকার।
আমার ঘরের পড়ার টেবিলে কয়েকদিন আগে পাড়ার লাইব্রেরী থেকে আনা ছোট গল্পের সংকলন বইটা পড়ে আছে। এ ক‘দিন খুলে দেখার সময় পাই নি। আজ আবার একটা নতুন গল্প পড়ব। তার নায়িকা জোছনা থাকবে না, হয় তো থাকবে কৃষ্ণা বা অন্য কেউ।
—০০০—
S13
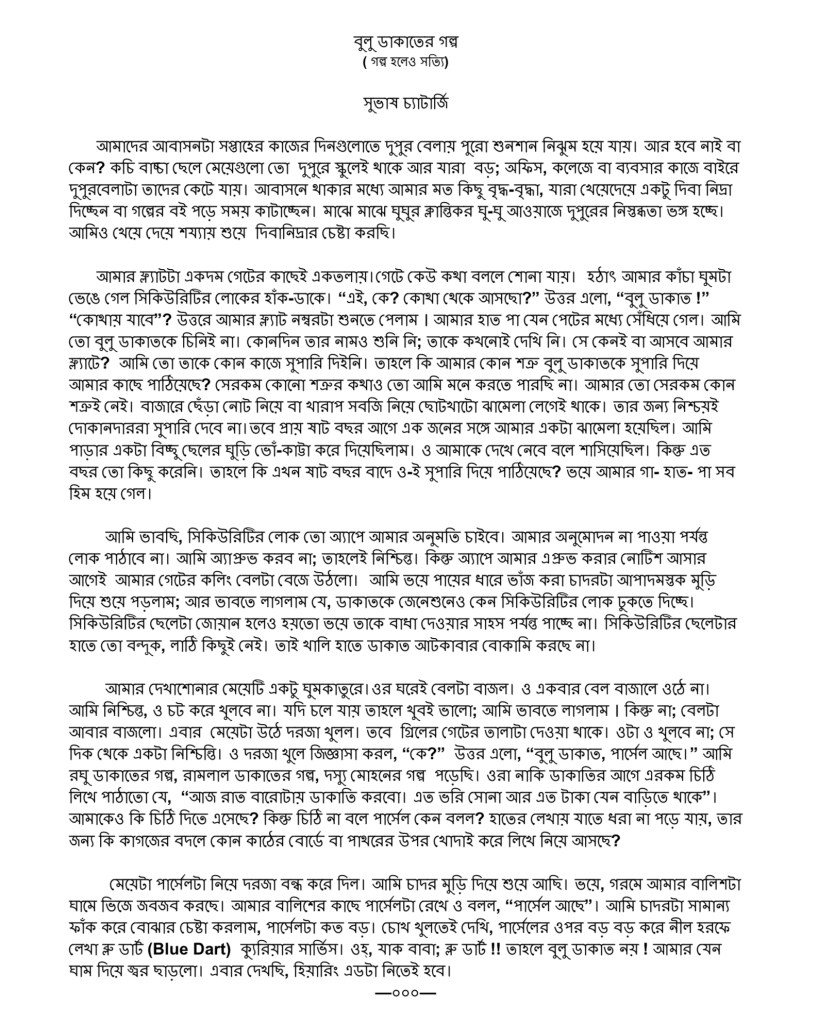
S14
ভবেনবাবুর ভোটভাবনা
সুভাষ চ্যাটার্জি
ভবেনবাবু ছাপোষা নিরীহ গৃহস্থ। কারো সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না। কোনো ভোটেও দাঁড়ান না।কোনো দলের মিছিলে, সমাবেশে যান না। তবে ভোটদানকে সুনাগরিকের কর্তব্য বলেই জ্ঞান করেন, তাই প্রত্যেকবার ভোটের সময় নিয়ম করে ভোট দিতে যান।দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে মুখে পান চিবোতে চিবোতে তিনি ভোটকেন্দ্রে যান, ঠিক যে সময় ভোটারদের ভিড় বেশ কম থাকে।
এই বিষয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বেশ মতবিরোধ ছিল। তাঁর স্ত্রী যখন জীবিত ছিলেন, তখন সক্কাল সক্কাল গিয়ে ভোট দিয়ে আসতেন,আর বলতেন, ‘‘বাব্বা, একটা বড় কাজ সারা হয়ে গেল। দেরী করলে কে কখন ভোটে থাবা বসায়, বলা তো যায় না। এখন নিশ্চিন্তে ধীরে সুস্থে ঘরের কাজ সারব। হ্যাঁ, একটু ভিড়ে লাইন দিতে হয় বটে, তার আর কি করা যাবে?একটা দিন বই তো নয়। দুপুরে খাওয়ার পর একটু বিশ্রামের সময়।ঐ সময় ভরপেটে রোদের মধ্যে রাস্তা ঠেঙিয়ে আমি বাপু যেতে পারব না।‘‘
ভবেনবাবু অবশ্য এতে আপত্তির কিছু দেখতে পান না। তিনি মনে করেন, এই ভিন্ন মতের সহাবস্থান হলো গণতান্ত্রিক পরিবেশের বহিঃপ্রকাশ। যত মত, তত পথ।আর ভোট নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ভিন্ন মত কি শুধু একটাই? তাঁর স্ত্রী ভোট দেন রমেশ ঘোষকে। ভবেনবাবু বলেন, “ওর নাম তো হওয়া উচিত রমেশ ঘুষ।ঘুষ ছাড়া তো উনি কোন কাজই করেন না।” আর তাঁর স্ত্রী বলেন, “আর তোমার পরমেশ বিশ্বাসের নাম তো পরমেশ অবিশ্বাস হলেই ভালো মানায়। তুমি ওকে যে কি করে বিশ্বাস কর, জানি নে বাপু।” ভবেনবাবুও অবশ্য তাকে বিশ্বাস করেন না; তবে তিনি বলেন, রাজনীতির লোকেরা কেউই ভালো নয়।তার মধ্যে যে কম খারাপ, তাকেই ভোট দেওয়া উচিত। কিন্তু কে যে কম খারাপ, তা নিয়ে বৌয়ের সাথে ভবেনবাবুর কোনদিনও মতের মিল হয় নি।
পাঁচ বছর হয়ে গেল ভবেনবাবুর স্ত্রী গত হয়েছেন। সেবার ডেঙ্গুর খুব প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। হঠাৎই কদিনের জ্বরে ডাক্তার বদ্যির সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তার স্ত্রী তাকে একলা ফেলে চলে গেছেন ।ভোট এলেই কেন জানি না ওঁর বৌয়ের কথা খুব মনে পড়ে। মতপার্থক্য যতই থাকুক, বৌ তো। সব বিষয়েই যদি মতের মিল হবে, তবে আবার কিসের স্বামী-স্ত্রী?
এই পাঁচ বছরে পাঁচ বার ভোট হয়েছে। লোকসভা, বিধানসভা, মিউনিসিপ্যালিটির তিনবারের ভোট তো আছেই, তার উপর আবার দুবার দুই নির্বাচিত প্রতিনিধির মৃত্যুর জন্য অন্তর্বর্তী ভোট। ভবেনবাবু প্রতিবারের মতো নিয়ম করে দুপুরে খাবার পর এবারও ভোট দিতে গেছেন। ভোটকেন্দ্রের সীমানায় পৌঁছে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছেন। ভীড় একদমই নেই। নিজের ভোটটা দিয়ে এসে আবার এপাশ ওপাশ দেখছেন। সামনের বেঞ্চে বসা বিভিন্ন দলের ছেলেদের মধ্যে একজন বলে উঠল,‘‘ কাকাবাবু, কাউকে খুঁজছেন?” ভবেনবাবু বললেন,‘‘ হ্যাঁ, মানে আমার স্ত্রী কি ভোট দিয়ে চলে গেছেন?” ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল,‘‘ হ্যাঁ, কাকিমা তো বেশ কিছুক্ষণ আগে ভোট দিয়ে গেছেন। এই তো নামের পাশে টিক দেয়া আছে।” ভবেনবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন,‘‘ তুমি ঠিক দেখেছ? আচ্ছা, কিরকম শাড়ি পরে এসেছিল?” ছেলেটি বলল, ‘‘কালো ডোরাকাটা”। ভবেনবাবু বিড়বিড় করে বললেন,‘‘ তাহলে হয় তো ঠিকই এসেছিল। ডেঙ্গুর মশার গায়ে তো শুনেছি, ওরকম কালো ডোরাকাটা দাগই থাকে।” ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, ‘‘কাকাবাবু, কিছু বলছেন?” ভবেনবাবু বললেন,‘‘ আমার সঙ্গে দেখা হল না। তোমার কাকিমা পাঁচ বছর আগে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন। কিন্তু প্রতি বছর নিয়ম করে ভোট দিয়ে কর্তব্য করে গেছেন। আমার সঙ্গে কোনবারই দেখা হয় নি। এবারও হোল না”।
View more
